ভূমিকা
বাকস্বাধীনতা গণতান্ত্রিক সমাজের একটি মূল ভিত্তি, যা বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোতে সুরক্ষিত। তবে, এই অধিকারটি নিরঙ্কুশ নয়; প্রায়শই বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য প্রতিরোধ করার প্রয়োজনের সাথে এর ভারসাম্য রক্ষা করা হয়, যা সহিংসতা এবং বৈষম্য উস্কে দিতে পারে। এই দুটি নীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি উল্লেখযোগ্য আইনি দ্বিধা তৈরি করে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, যেখানে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা এবং বিধিবদ্ধ আইন এই ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।
বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো
বাংলাদেশের সংবিধানে বাকস্বাধীনতা
বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে:
“(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা, অথবা আদালতের অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কিত যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হইল।”
সুতরাং, বাকস্বাধীনতা সুরক্ষিত হলেও, এই অধিকারের অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে এটি প্রয়োগ করা হয়।
বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি বিধান
সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি আইন বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যকে সীমিত করে:
● দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ১৫৩এ এবং ২৯৫এ ধারা বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতিগত বা ভাষাগত গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা প্রচার করে এমন কাজগুলোকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।
● ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ – ২৫ এবং ২৮ ধারা অনলাইনে আপত্তিকর বিষয় প্রকাশ করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে, যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে।
● তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইন, ২০০৬ – ৫৭ ধারা (বর্তমানে বাতিল) কর্তৃপক্ষের ক্ষতিকর বলে বিবেচিত বক্তব্যকে জনশৃঙ্খলা বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হিসেবে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে ব্যবহৃত হতো।
বাকস্বাধীনতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনি মানদণ্ড
মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) বাকস্বাধীনতা স্বীকার করে, তবে বক্তব্য সহিংসতা বা বৈষম্য উস্কে দিলে সীমাবদ্ধতার অনুমতি দেয়।
আইসিসিপিআর-এর ১৯ অনুচ্ছেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে, তবে “অন্যদের অধিকার বা খ্যাতি রক্ষার জন্য” বা “জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য” প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের অনুমতি দেয়।
আইসিসিপিআর-এর ২০(২) অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে রাষ্ট্রগুলোকে “জাতীয়, জাতিগত বা ধর্মীয় বিদ্বেষের যেকোনো প্রচার যা বৈষম্য, শত্রুতা বা সহিংসতার প্ররোচনা করে” নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে।
বাকস্বাধীনতা বনাম বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের উপর বিচারিক দৃষ্টিকোণ
বাংলাদেশের বিচারিক দৃষ্টিকোণ
বাংলাদেশের বিচার বিভাগ বাকস্বাধীনতার সীমানা ব্যাখ্যা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বনাম বাংলাদেশ সরকার (২০১০) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জোর দিয়েছিল যে বাকস্বাধীনতা অপরিহার্য, তবে এটি জনশৃঙ্খলা ব্যাহত করা উচিত নয়।
আরেকটি উল্লেখযোগ্য মামলা, বাংলাদেশ বনাম অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খান (২০১৮), একাডেমিক স্বাধীনতা এবং এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করেছে, যেখানে আদালত রায় দিয়েছিল যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উস্কে দেওয়া বক্তব্য বাকস্বাধীনতার অধীনে সুরক্ষিত হতে পারে না।
আন্তর্জাতিক মামলার আইন
● শেনক বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯১৯) – বিচারপতি অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস “স্পষ্ট এবং বর্তমান বিপদ” পরীক্ষা চালু করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে বক্তব্য যদি আসন্ন হুমকি তৈরি করে তবে তা সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে।
● ব্র্যান্ডেনবার্গ বনাম ওহিও (১৯৬৯) – মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে অবৈধ আচরণ সমর্থনকারী বক্তব্য সুরক্ষিত, যদি না এটি আসন্ন বেআইনি পদক্ষেপকে উস্কে দেয়।
● জার্সিল্ড বনাম ডেনমার্ক (১৯৯৪) – ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত রায় দিয়েছে যে বর্ণবাদীদের সাথে একজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার সীমাবদ্ধ করা মানবাধিকারের ইউরোপীয় কনভেনশনের ১০ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে, যা বাকস্বাধীনতা এবং জনস্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য তুলে ধরে।
বাকস্বাধীনতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করার চ্যালেঞ্জ
বাকস্বাধীনতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করা একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ, কারণ এতে মতামত প্রকাশের অধিকারের সাথে ব্যক্তি ও সমাজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনের ভারসাম্য রক্ষা করা জড়িত। আইনবিদ রোনাল্ড ডওয়ারকিন অতিরিক্ত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন, যুক্তি দেন যে “বাকস্বাধীনতা বৈধ সরকারের একটি শর্ত” এবং বিস্তৃত সীমাবদ্ধতা গণতান্ত্রিক আলোচনাকে দমন করতে পারে। বিপরীতে, আইনবিদ জেরেমি ওয়ালড্রন ক্ষতির নীতি প্রয়োগ করে যুক্তি দেন যে সামাজিক ক্ষতি করে এমন বক্তব্য সীমিত করা উচিত। এই বিতর্কটি কেবল আইনি নয়, নৈতিক ও ধর্মতাত্ত্বিকও। সেন্ট অগাস্টিন সতর্ক করেছিলেন, “কেউ না করলেও সঠিক সঠিক; সবাই করলেও ভুল ভুল,” ক্ষতিকর বক্তব্য বোঝার নৈতিক দায়িত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। বিএলএএসটি বনাম বাংলাদেশ (২০০৩) মামলায়, বাংলাদেশ হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের অধীনে বাকস্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার, তবে মানহানি, আদালতের অবমাননা বা জনশৃঙ্খলা উদ্বেগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। একইভাবে, ইসলামিক পণ্ডিত আল-গাজ্জালী জোর দিয়েছিলেন, “কথা বলার আগে কথাগুলো আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু একবার বললে আপনি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসেন,” যা বক্তব্যের সাথে আসা দায়িত্বকে তুলে ধরে। এই ধর্মতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টিগুলো এই ধারণাকে শক্তিশালী করে যে বক্তব্য নৈতিক দায়িত্বের সাথে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে এটি বিদ্বেষ এবং ক্ষতির দিকে না যায়।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: অধিকার এবং দায়িত্বের ভারসাম্য
বাংলাদেশ, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সমর্থন করে। এই অধিকারটি দেশের সংবিধানে ৩৯ অনুচ্ছেদের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা চিন্তা, বিবেক এবং বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। যাইহোক, এই অধিকারটি নিরঙ্কুশ নয়, কারণ সরকার সামাজিক সম্প্রীতি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে কিছু আইনি বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এই ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি হলো বাকস্বাধীনতার সাথে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য প্রতিরোধের প্রয়োজনের ভারসাম্য রক্ষা করা, বিশেষ করে দ্রুত বিকাশমান ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপে।
সামাজিক মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর উত্থান ব্যক্তিদের তাদের মতামত প্রকাশ করা সহজ করে তুলেছে। যাইহোক, এটি ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য ছড়ানোর জন্য নতুন পথ তৈরি করেছে। বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য, যার মধ্যে ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা অন্যান্য পরিচয়ের ভিত্তিতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, বৈষম্য বা শত্রুতা উস্কে দেয় এমন অভিব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত, বাংলাদেশের সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি তৈরি করে। দেশের বৈচিত্র্যময় এবং প্রায়শই রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত পরিবেশের কারণে, অনিয়ন্ত্রিত বক্তব্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, সামাজিক অস্থিরতা এবং এমনকি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।
এই উদ্বেগগুলো মোকাবেলার জন্য, বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি আইনি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই আইনটি সাইবার অপরাধ দমন, বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য প্রতিরোধ এবং নাগরিকদের ডিজিটাল হয়রানি থেকে রক্ষা করার জন্য চালু করা হয়েছিল। ডিএসএ একটি নিরাপদ ডিজিটাল স্থান তৈরি করার উদ্দেশ্যে করা হলেও, এর অপরাধের সংজ্ঞা অত্যধিক বিস্তৃত এবং অস্পষ্ট হওয়ার জন্য ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে, বিশেষ করে সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী এবং বিরোধী কণ্ঠের বিরুদ্ধে অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।
সমালোচকরা যুক্তি দেন যে ডিএসএ বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষার পরিবর্তে সেন্সরশিপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যেখানে সাংবাদিক এবং সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারকারীসহ ব্যক্তিদের সরকার বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশের জন্য এই আইনের অধীনে গ্রেপ্তার বা হয়রানি করা হয়েছে। এর ফলে, ভিন্নমত দমন এবং বাংলাদেশে মুক্ত মত প্রকাশের স্থান সঙ্কুচিত হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারকে ডিএসএ সংশোধন বা বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছে, জোর দিয়ে বলেছে যে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য দমনের জন্য তৈরি করা আইনগুলো বিরোধী কণ্ঠকে নীরব করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। তারা যুক্তি দেয় যে একটি সুষম আইনি কাঠামো সামাজিক সম্প্রীতির জন্য প্রকৃত হুমকি এবং সমালোচনার বৈধ অভিব্যক্তিগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। চ্যালেঞ্জটি হলো এমনভাবে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য সংজ্ঞায়িত করা যা বাকস্বাধীনতাকে লঙ্ঘন না করে, কিন্তু কার্যকরভাবে সহিংসতা এবং বৈষম্যের প্ররোচনা প্রতিরোধ করে।
বাকস্বাধীনতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য নিয়ন্ত্রণের বিতর্ক একটি নৈতিক এবং নৈতিক বিতর্কও। ধর্মতত্ত্ববিদ এবং দার্শনিকরা দীর্ঘকাল ধরে দায়িত্বশীল বক্তব্যের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামিক পণ্ডিত আল-গাজ্জালী সতর্ক করেছিলেন, “কথা বলার আগে কথাগুলো আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু একবার বললে আপনি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসেন।” এটি বক্তব্যের শক্তি এবং ব্যক্তিদের দায়িত্বের সাথে এটি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। একইভাবে, খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ডিয়েটরিখ বনহোফার যুক্তি দিয়েছিলেন যে “অন্যায়ের মুখে নীরবতা নিজেই অন্যায়,” যা সমাজে ভিন্নমত এবং গঠনমূলক সমালোচনার জন্য স্থান দেওয়ার গুরুত্বকে তুলে ধরে।
একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির জন্য সুপারিশসমূহ:
১. ঘৃণা ভাষণ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা – আইনগুলিকে বৈধ সমালোচনা এবং সহিংসতা উস্কে দেওয়া বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত।
২. বিচার বিভাগীয় তত্ত্বাবধান – আইনি বিধানের অপব্যবহার রোধ করতে ঘৃণা ভাষণের মামলাগুলো পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে আদালতগুলোর সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত।
৩. জনসচেতনতা ও শিক্ষা – বাক স্বাধীনতার অধিকার এবং দায়িত্বশীল আলোচনার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ঘৃণা ভাষণের সমস্যা কমাতে পারে।
৪. আইনি সংস্কার – ক্ষতিকর বক্তব্য থেকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা বজায় রেখে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো আইনগুলোর অপব্যবহার রোধ করতে সংশোধন করা।
৫. নৈতিক সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করা – ভুল তথ্য এবং চাঞ্চল্যকরতা রোধ করতে সাংবাদিকদের নৈতিক রিপোর্টিং মান বজায় রাখার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৬. স্বচ্ছ আইন প্রয়োগ – আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যেন নিরপেক্ষভাবে এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই বক্তব্য সম্পর্কিত আইন প্রয়োগ করে তা নিশ্চিত করা।
৭. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা – মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করে ঘৃণা ভাষণের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নীতি প্রয়োগ করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে সহযোগিতা করা।
৮. সম্প্রদায়গত সম্পৃক্ততা উদ্যোগ – সহনশীলতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সম্প্রদায় পর্যায়ে সংলাপ এবং আলোচনাকে উৎসাহিত করা।
৯. হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা জোরদার করা – ঘৃণা ভাষণ রিপোর্ট করে এমন ব্যক্তিদের প্রতিশোধ বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করা নিশ্চিত করা।
১০. স্বাধীন তদারকি সংস্থা তৈরি করা – সরকারি প্রভাব ছাড়াই বাক স্বাধীনতা এবং ঘৃণা ভাষণের মামলাগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা।
১১. পাল্টা বক্তব্যকে উৎসাহিত করা – উত্তেজনা কমাতে এবং সম্মানজনক আলোচনাকে উৎসাহিত করতে ঘৃণা ভাষণের বিরুদ্ধে ইতিবাচক এবং পাল্টা আখ্যান প্রচার করা।
১২. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা – বাংলাদেশের বাক স্বাধীনতা এবং ঘৃণা ভাষণ নিয়ন্ত্রণ উন্নত করতে বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম অনুশীলন থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা করা।
উপসংহার:
বাক স্বাধীনতা এবং ঘৃণা ভাষণের মধ্যে উত্তেজনা বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাপী একটি চলমান আইনি দ্বিধা তৈরি করে। সাংবিধানিক সুরক্ষা বাক স্বাধীনতাকে রক্ষা করলেও, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আইনি বিধিনিষেধ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বিচারশাস্ত্র এবং দেশীয় আইনি সংস্কার দ্বারা অবহিত একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং জনশৃঙ্খলা উভয়ই নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
Footnotes:
1. Bangladesh Constitution
- Constitution of the People’s Republic of Bangladesh, art 39
2. Bangladeshi Legal Framework on Hate Speech
- Penal Code 1860 (Bangladesh), ss 153A, 295A
- Digital Security Act 2018 (Bangladesh), ss 25, 28
- Information and Communication Technology Act 2006 (Bangladesh) (repealed), s 57
3. International Human Rights Treaties and Declarations
- UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights (adopted 10 December 1948) UNGA Res 217 A(III), art 19
- International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171, arts 19, 20(2)
4. Bangladeshi Case Law
- Bangladesh Nationalist Party v Government of Bangladesh (2010)
- Bangladesh v Professor Morshed Hasan Khan (2018)
- BLAST v Bangladesh (2003)
5. International Case Law on Free Speech and Hate Speech
- Schenck v United States 249 US 47 (1919)
- Brandenburg v Ohio 395 US 444 (1969)
- Jersild v Denmark App no 15890/89 (ECtHR, 23 September 1994)
6. Legal and Political Theories on Free Speech
- Ronald Dworkin, Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution (Harvard University Press 1996)
- Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech (Harvard University Press 2012)
7. Philosophical and Theological Perspectives
- Saint Augustine, The City of God (c 426 AD)
- Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din (11th century)
- Dietrich Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison (1951)
8. Reports from Human Rights Organizations
- Human Rights Watch, Bangladesh: Repeal Abusive Digital Security Act (HRW 2022)
- Amnesty International, Censorship and the Digital Security Act in Bangladesh (Amnesty International 2023)
9. Media and Policy Analysis
- ‘How Bangladesh’s Digital Security Act is Being Used for Censorship’ The Daily Star (Dhaka, 10 March 2023) https://www.thedailystar.net accessed 19 April 2025
- ‘The Impact of the Digital Security Act on Free Speech in Bangladesh’ Dhaka Tribune (Dhaka, 15 December 2023) https://www.dhakatribune.com accessed 19 April 2025

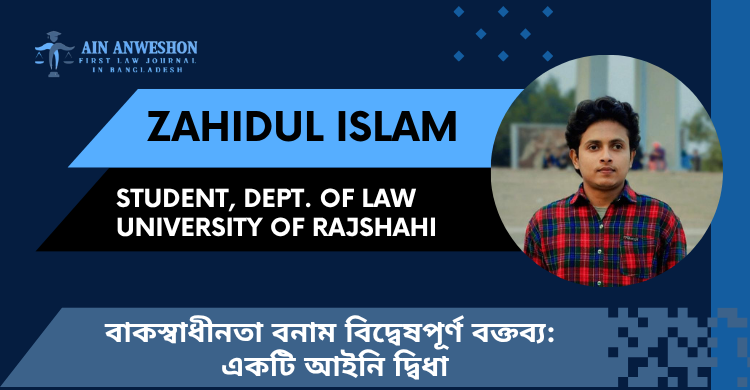


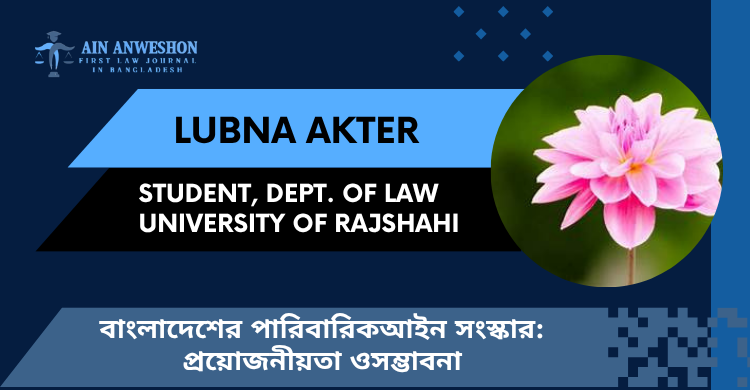




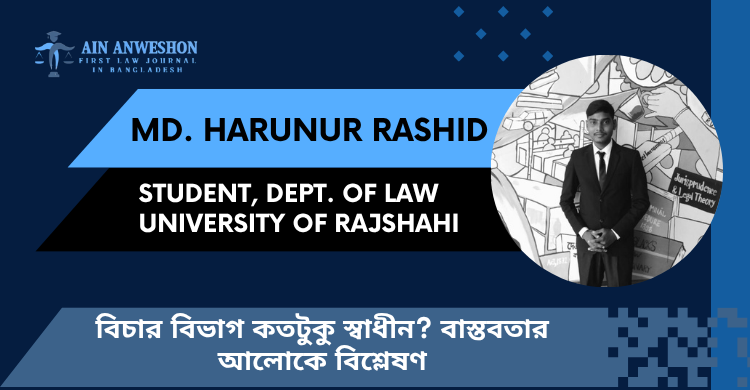







One Response
অনেক সুন্দর লেখা এবং লেখার ভাষা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা রইলো