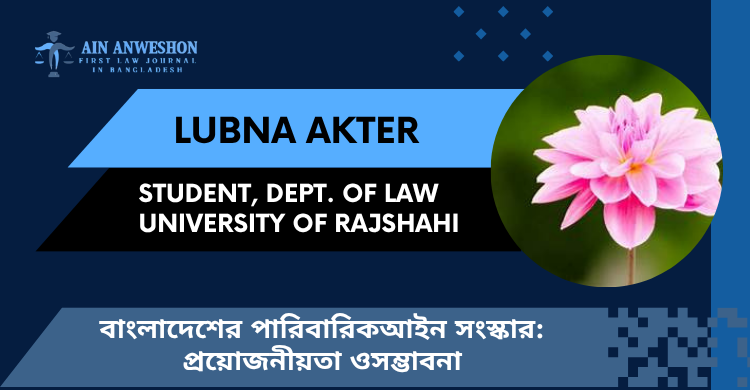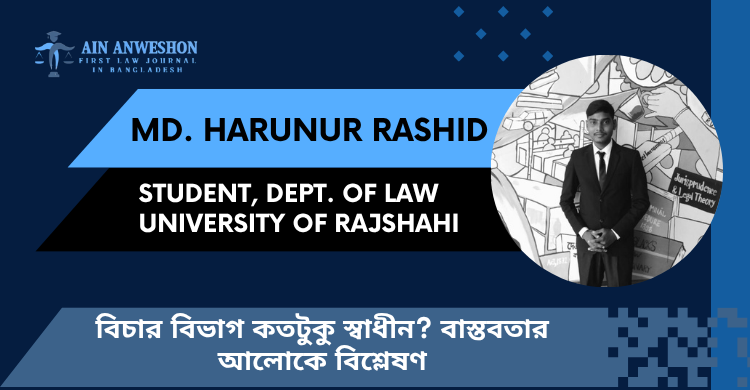১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেও, সংবিধানিক কাঠামো এখনো বিকাশমান ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। জাতির মূল দলিল ১৯৭২ সালের সংবিধানটি বহুবার সংশোধিত হয়েছে, যা দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও সামাজিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। বর্তমান সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা মূলত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের দিকে পথ খোঁজার ওপর কেন্দ্রীভূত, যেখানে দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে।
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালীকরণ:
গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশকে একটি দৃঢ় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তর করার প্রয়াস চলছে। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, বিচার বিভাগের সংস্কার, এবং নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার দাবিগুলো দিন দিন জোরালো হচ্ছে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ রোধ এবং শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য কার্যকর ‘চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স’-এর প্রয়োজনীয়তা আজ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।
অন্তর্ভুক্তির প্রয়াস
সংবিধান সংস্কারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তি ও সুরক্ষা। একটি বহুজাতিক সমাজ হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানে সকল সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সামাজিক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার স্বীকৃতি, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা, এবং ঐতিহাসিক বঞ্চনার নিরসনের লক্ষ্যে নতুন করে ভাবনার সময় এসেছে। সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আহ্বান ক্রমাগত জোরালো হচ্ছে।
মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা:
যদিও ১৯৭২ সালের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে, বাস্তবে তা প্রায়শই বাস্তবায়নের ঘাটতিতে পড়েছে। বিশেষ করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টসহ বিভিন্ন আইন এ স্বাধীনতাগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। তাই নিরাপত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি এখন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মীয় পরিচয়:
রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র নিয়েও বিতর্ক আছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল ধর্মনিরপেক্ষ নীতিমালা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে, যার ফলে এখন ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবনার দরকার দেখা দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় পরিচয় এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার – এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন একটি জটিল অথচ অত্যাবশ্যক বিষয়।
পূর্ববর্তী সংশোধনসমূহের পুনর্মূল্যায়ন:
সংবিধানের বহুবার সংশোধন তার মৌলিক চেতনার ওপর কী প্রভাব ফেলেছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই একটি জাতীয় সংবিধান কমিশন গঠনের পক্ষে, যা পূর্ববর্তী সংশোধনসমূহ পর্যালোচনা করে একটি জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংস্কার প্রস্তাব করবে। এতে করে জনগণের সংবিধানের প্রতি আস্থা ফিরে আসতে পারে এবং এটি বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
একটি জাতীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা:
একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হতে হলে বিস্তৃত জাতীয় সংলাপ অপরিহার্য। এতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, আইনবিদ, এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও সবাইকে শোনা যাবে এমন, যাতে সংবিধান সংস্কার সত্যিকার অর্থেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়।
চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবায়নের প্রশ্ন:
তবে পথটি সহজ নয়। রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস গঠনমূলক সংলাপের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সংলাপের সংস্কৃতি এবং সহনশীল রাজনীতির চর্চা জরুরি। শুধু আইন পাশ করলেই হবে না; তার কার্যকর বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে, নইলে তা কাঙ্ক্ষিত ফল আনবে না।
উপসংহার:
বাংলাদেশে সংবিধান সংস্কারের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট এ দেশের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের সন্ধানে চলমান পথচলার প্রতিফলন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, অন্তর্ভুক্তি, মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রের চরিত্র সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে সংস্কার সাধন করে বাংলাদেশ একটি আরো ন্যায়ভিত্তিক, সমতাপূর্ণ ও টেকসই রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজন অবিচল প্রতিশ্রুতি, মুক্ত সংলাপ এবং একটি অভিন্ন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি।