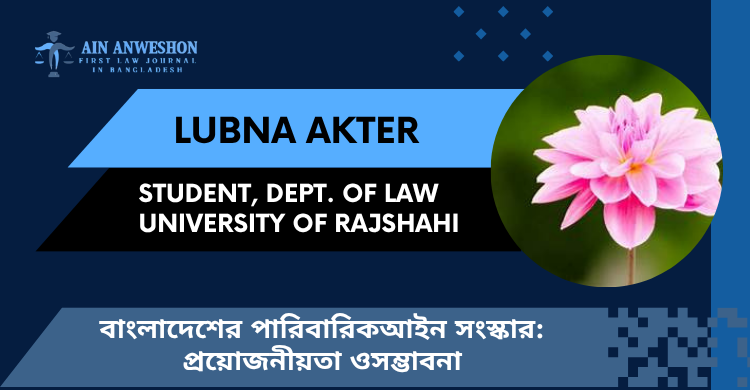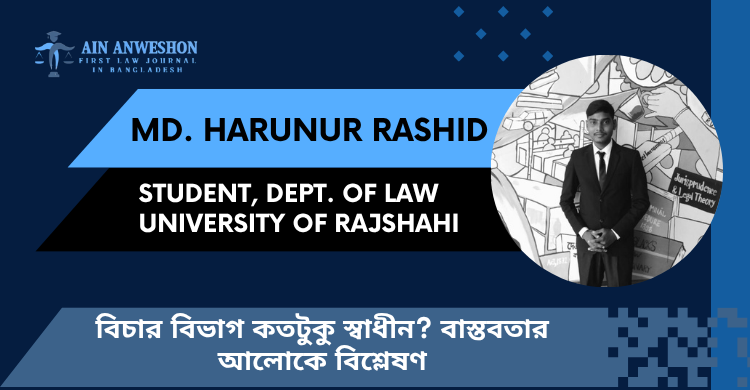ভূমিকা
সমাজতান্ত্রিক একটি বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে তুলে ধরে। যেখানে ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর সমাজতন্ত্রকে সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্যায় হিসেবে ধরা হয়।স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের শাসন মুক্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র সংযুক্ত করা হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার হাত থেকে বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনসংখ্যা কে রক্ষা করাই হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। মূল সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে অবস্থান থাকলেও ১৯৭৯ সালের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে শুধুমাত্র ‘অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার’ অর্থে এর বিয়োযোজন ঘটানো হয়। এবং ২০১১ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে (আর্টিকেল ১০-এ) পুন:স্থাপিত করা হয়। যা বাংলাদেশের সংবিধানের সাম্যবাদী ধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।
সমাজতন্ত্রের মূল মন্ত্র
সমাজতন্ত্রের মূলনীতি হল ‘প্রত্যেকে কাজ করবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেকে ব্যবহার করবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।’^১ এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার সঞ্চিত বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদ সমাজ বা রাষ্ট্রকে দিতে বাধ্য থাকে। রাষ্ট্র বা সমাজ এসব সম্পদ প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের নিকট হস্তান্তর করে।সমাজতন্ত্র বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সংকট দূরীকরণের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিত করে। পুঁজিবাদী সমাজ যেখানে বৈষম্য, শোষণ ও অত্যাচার নিশ্চিত করছে ; এর বিপরীতে সমাজতন্ত্র সমাজের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করছে। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, “আমার মতে, বর্তমান কালের সংকটের মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক নৈরাজ্য। … … আমি নিশ্চিত, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই মন্দ দিকগুলো দূর করা যেতে পারে; সেইসঙ্গে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার যার উদ্দেশ্য হবে একটি সামাজিক লক্ষ্য স্থির করা। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের মালিকানায় থাকবে সমাজ এবং উৎপাদনের ফল পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার হবে। একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি, যেটি সমাজের প্রয়োজনের জন্য উৎপাদনের সমন্বয় করবে, প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তির কর্মকে সমভাবে বিতরণ করবে এবং পুরুষ-নারী ও শিশু নির্বিশেষে জীবনধারণের উপায় সুনিশ্চিত করবে। সহজাত উৎকর্ষ এবং সামর্থ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যক্তির শিক্ষা তার সামাজিক দায়বোধের চিন্তাভাবনা জাগাবে। বর্তমানে যে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সাফল্যের সোপান হিসেবে শিক্ষাকে তুলে ধরা হয়, উল্লেখিত ব্যবস্থা হবে তার বিপরীত।”^২
রাজনৈতিক নেতাদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা
১৮৭১ সালে কলকাতার একটি দল কার্ল মার্ক্সের সাথে যোগাযোগ করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনালের একটি শাখা সংগঠন করা।৩^ ভারতীয় ভাষায় কার্ল মার্ক্সের প্রথম জীবনী রচনা করেন আর. রামকৃষ্ণ পিল্লাই ১৯১৪ সালে।৪^ ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে বিভিন্ন নেতারা, যেমন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভগৎ সিং, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন।১৯২৫ সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) গঠিত হয়েছিল, যা সরাসরি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রচার করেছিল এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিল।ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ১৯৩১ সালের করাচি অধিবেশনে উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ন কে ভারতের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।^৫ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নীতি গ্রহণের কথা বলতেন এবং জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দেন। স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেন।রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এবং মিশ্র অর্থনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে তিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। পাকিস্তানেও স্বাধীনতার পর কিছু বামপন্থী আন্দোলন দেখা যায়, যদিও সামরিক এবং রক্ষণশীল শাসনের কারণে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সেখানে তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের নেতারা যেমন শেখ মুজিবুর রহমান, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন। তিনি “রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতি” এবং “বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র” প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন।
বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলো, যেমন কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাসদ, স্বাধীনতার পর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সমাজতন্ত্র
বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় চারটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ও সমাজতন্ত্র।^৬
বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
‘১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করা।’^৭ এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো শ্রেণী বৈষম্য দূর করে একটি সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।“এই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হইবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।”^৮ এখানে সমাজতন্ত্র বলতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে একটি অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা বোঝানো হয়েছে। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ড. কামাল হসোন বলেন,”রাষ্ট্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের সকল প্রকার অবসান সাধন করিতে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া গণমানুষের জন্য একটি শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”^ ৯
১৯৭৯ সালে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জিয়াউর রহমান সমাজতন্ত্রের অর্থের পরিবর্ত ঘটান। কিন্তু ২০১১ সালে আবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে সমাজতন্ত্রকে পুণঃস্থাপন করে। ‘১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীতে সমাজতন্ত্রের নীতির কিছু পরিবর্তন আসে এবং ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই নীতি পুনরায় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।’^১০
সংবিধান অনুসারে সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা
বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটি হলো সমাজতন্ত্র। বৃহৎ অর্থে সমাজতন্ত্র বোঝানো না হলেও মূলত এটি অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। যাতে করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা পায়। যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বর্তমান বাংলাদেশ সময় পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের এই মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। জন-মানুষের প্রত্যাশা , সংবিধানের এই সমাজতন্ত্র অনেকাংশ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বা হচ্ছে। সংবিধানে উল্লেখিত সমাজতন্ত্রের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর বাস্তবায়নে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সকল সীমাবদ্ধতা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত।
যেমন:
১. অর্থনৈতিক বৈষম্য :
সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।আমাদের দেশে ধনী গরিবের পরস্পর সহযোগিতা কিংবা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা চলছেও তা যথাযথ পর্যায়ে সফলতা পাচ্ছে না। বাংলাদেশে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত, তা মূলত মিশ্র অর্থনীতি। এখানে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উপাদান দুটোই মিশে আছে। সরকার বিভিন্ন খাতে মিশ্র নীতি গ্রহণ করেছে—যেখানে কিছু সেক্টর সরকার পরিচালিত, যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা, এবং কিছু সেক্টর ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত, যেমন বাণিজ্য ও শিল্প। এর ফলে বর্তমান বাংলাদেশে এক শ্রেণীর মানুষ প্রতিনিয়ত সম্পদশালী হচ্ছে এবং এক শ্রেণীর মানুষ প্রতিনিয়ত শোষিত হয়ে দারিদ্র্যের নিম্নসীমায় বসবাস করছে। “বাংলাদেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা।সম্পদের সুষম বণ্টন এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।”^১১ আমরা যদি আমাদের শহর ও গ্রাম গুলোর দিকে তাকাই তাহলে বৈষম্যটা স্পষ্ট বোঝা যায়।দেখা যাচ্ছে যে শহরে বসবাসরত মানুষ যেসব সুযোগ-সুবিধা পায় তা থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ অনেকাংশই বঞ্চিত। যথাযথ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার অভাবে গ্রামনের মানুষ গুলো জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা তো দূর, দিন দিন তারা আরো পিছিয়ে পড়ছে।
২. রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতি:
রাজনীতি একটি বাংলা শব্দ। এর ব্যাস বাক্য হলো রাজার নীতি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বলে, যারাই ক্ষমতায় আসে তারাই কোন না কোন ভাবে তাদের শাসন ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়। যার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূর্নীতির কালো ছায়া নেমে আসে। যে সমাজ বা রাষ্ট্রে দূ্রনীতির মত অভিশাপ থাকবে সেখানে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।
“রাজনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য পূরণে বাধা সৃষ্টি করে।
রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে কাজ করে, যা সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলোর বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।”^১২ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হবে। এর জন্য দরকার যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা এবং রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যকার পরমতসহিষ্ণুতা।
৩. মিশ্র অর্থনীতি ও বেসরকারিকরণ:
বেসরকারিকরণ এবং মিশ্র অর্থনীতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ধারণা।
★ বেসরকারিকরণ হল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা সম্পদের বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া। এটি সাধারণত সরকারের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারি সংস্থা বা কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আরও দক্ষ এবং লাভজনক করার উদ্দেশ্যে ঘটানো হয়। বেসরকারিকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং সেবার গুণমান উন্নত হতে পারে। এটি সরকারী সংস্থাগুলির ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করে, যা কর্মসংস্থান, প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নকে আরও উৎসাহিত করে।
★ মিশ্র অর্থনীতি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা যেখানে বেসরকারি খাত এবং সরকারি খাত একসঙ্গে কাজ করে। এই ব্যবস্থায় সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে নিয়ন্ত্রণ রাখে, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন ইত্যাদি, এবং অন্যান্য খাতগুলোতে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করে। মিশ্র অর্থনীতি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি, যেখানে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের শক্তি এবং সক্ষমতাগুলি একত্রিত করা হয়। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যা উভয় খাতের মধ্যে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে।
“বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে একটি মিশ্র অর্থনীতিতে পরিচালিত হয়, যেখানে বেসরকারি খাতের ভূমিকা ক্রমশ বাড়ছে। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও বেসরকারিকরণ এবং বাজার অর্থনীতির কারণে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন কঠিন।”^১৩ মিশ্র অর্থনীতি এবং বেসরকারিকরণের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কার্যকর করা হচ্ছে। একটা দেশের সমগ্র উন্নয় এবং উৎপাদনের উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তথা মিশ্র অর্থনীতির অস্বীকার করা যায় না।
৪. সামাজিক সচেতনতার অভাব:
সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে আইন থাকা সত্ত্বেও তারা প্রায়ই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত।”^১৪
বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে সাম্য, ন্যায়বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সমাজের অনেক মানুষ এখনও সমাজতন্ত্রের মূল ধারণা এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে অবগত নয়। এই সচেতনতার অভাব প্রধানত শিক্ষা, রাজনৈতিক বিভাজন এবং মিডিয়ার অপর্যাপ্ত প্রচারের কারণে হয়। এর ফলে, জনগণ সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল বুঝতে পারেন না, যা এর বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এছাড়া, রাজনৈতিক নেতাদের সঠিক প্রয়োগের অভাব এবং আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহও জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব সৃষ্টি করে, যা সমাজতন্ত্রের সফল বাস্তবায়নকে কঠিন করে তোলে।
৫. প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা:
বাংলাদেশে প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়নে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা প্রশাসনিক কার্যক্রমকে অকার্যকর করে, ফলে সমাজতান্ত্রিক নীতির সঠিক প্রয়োগ সম্ভব হয় না। দুর্নীতি, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থা প্রশাসনিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যদি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যথাযথ প্রশিক্ষিত না হন বা রাজনৈতিক প্রভাব তাদের কাজের ওপর পড়ে, তবে প্রশাসন জনগণের কল্যাণে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না। এসব প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার কারণে সমাজতন্ত্রের নীতির বাস্তবায়ন জটিল হয়ে যায়।
“প্রশাসনিক কাঠামোর অদক্ষতা এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় রাষ্ট্রের সম্পদ দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে নষ্ট হয়।”^১৫
৬. জনসংখ্যার চাপে সম্পদ সীমাবদ্ধতা:
“বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের ঘাটতি রয়েছে। ফলে সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য—প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা—বাস্তবে অর্জন করা কঠিন।”^১৬
একটি দেশের জনসংখ্যা যখন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়, তখন সে দেশের সীমিত সম্পদগুলোর উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপই হলো জনসংখ্যার চাপে সম্পদ সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশ একটি ঘন প্রস্তুতিপূর্ণ জনসংখ্যার দেশ। তাই এ দেশে জনসংখ্যার থেকে সম্পদের পরিমাণ খুবই কম। একদিকে জনসংখ্যা বেশি আবার অন্যদিকে সম্পদের পরিমাণ কম হওয়ায় সমাজতন্ত্রের সাম্য নীতি বাস্তবায়িত হতে বাধার সৃষ্টি করছে। সমস্যা সমাধানের জন্য অতিরিক্ত জনসংখ্যা কে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে এবং সম্পদের সাথে সাথে সুযোগের যথাসম্ভব সমতা রাখার চেষ্টা করতে হবে।
৭. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সীমাবদ্ধতা:
বাংলাদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সীমাবদ্ধতা সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়নে বড় বাধা। শিক্ষার আলো ছাড়া সচেতনতা বা উন্নতি কোনটাই সম্ভব নয়! শিক্ষা খাতে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে, বিশেষত গ্রাম ও শহরের মধ্যে। এর ফলে, অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা মানসম্পন্ন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। সরকারি স্কুলগুলোর অবকাঠামো দুর্বল, শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব এবং শিক্ষার মানের প্রতি অবহেলা রয়েছে। অধিকাংশ স্কুলে আধুনিক শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগও সীমিত, যা শিক্ষার মানের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে।
স্বাস্থ্য খাতেও একই ধরনের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। দেশে প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সের অভাব, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সংকট এবং স্বাস্থ্যসেবার মানের দুর্বলতা রয়েছে। সরকারি বরাদ্দ কম থাকায়, বেসরকারি খাতের প্রভাব বেশি, ফলে দরিদ্র জনগণ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। এসব সীমাবদ্ধতা সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য—সমাজে ন্যায়বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা—বাস্তবায়নকে কঠিন করে তোলে। তবে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে এসব সীমাবদ্ধতা দূর হলে, সমাজে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।
“শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর প্রধান স্তম্ভ। তবে, এই দুটি খাতে এখনও বৈষম্য রয়ে গেছে।”^১৭ আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনও মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত।
উপসংহার
বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি এবং তা সামাজিক ন্যায়বিচার ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের মধ্যে সাম্য এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, যা শোষণমুক্ত সমাজের ভিত্তি তৈরি করবে। তবে স্বাধীনতার পর থেকেই সমাজতন্ত্রের আদর্শের বাস্তবায়নে নানা বাধা সৃষ্টি হয়েছে, যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, এবং প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা। এসব সমস্যার কারণে সমাজতন্ত্রের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এখনো অর্জিত হয়নি। তবে, বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপন এবং রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলন কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি সুসংগঠিত এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি। সঠিক রাজনৈতিক ইচ্ছা, প্রশাসনিক দক্ষতা, এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, এবং বাংলাদেশে শোষণমুক্ত ও সাম্যভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
তথ্যসূত্র
- খারিস সাবিরভ; কমিউনিজম কী; প্রগতি প্রকাশন মস্কো; পৃষ্ঠা- ৩৩৮; ১৯৮৮।
- Why Socialism? by Albert Einstein, Monthly Review, May 1949.
- M.V.S Koteswara Rao, Communist Parties an United Fornt – experience in Kerala and West Bengal. Hyderabad : Parajasakti Book house, 2003. P-103
- M.V.S Koteswara Rao, Communist Parties an United Fornt – experience in Kerala and West Bengal. Hyderabad : Parajasakti Book house, 2003. P-82
- “The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development: The Case of India: Patterns of Change in the Legal System and Socio-Economy” (PDF). Cid.harvard.edu. Retrieved 28 July 2016.
- বাংলাদেশের সংবিধান, প্রস্তাবনা।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান- ৮ (২) অনুচ্ছেদ।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-অনুচ্ছেদ নং ১০।
- “বাংলাদেশের সংবিধান: মূলনীতি ও ব্যাখ্যা” – ড. কামাল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা।
- বাংলাদেশের সংবিধান, পঞ্চদশ সংশোধনী।
- Rahman, M. (2018). “Economic Inequality and Socialist Principles in Bangladesh”. Dhaka Journal of Economics, 25(3), 45-67।
- Transparency International Bangladesh (TIB) রিপোর্ট, ২০২৩।
- BIDS গবেষণা প্রতিবেদন, ২০২২।
- Khan, A. (2017). “Social Justice in the Constitution of Bangladesh”. Asian Journal of Political Science, 29(2), 89-102।
- Governance Report by UNDP Bangladesh, 2021।
- Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 2023।
- UNESCO Education Report on Bangladesh, 2022।