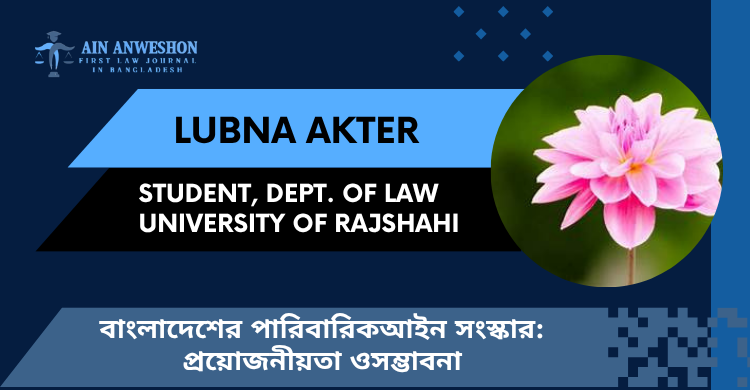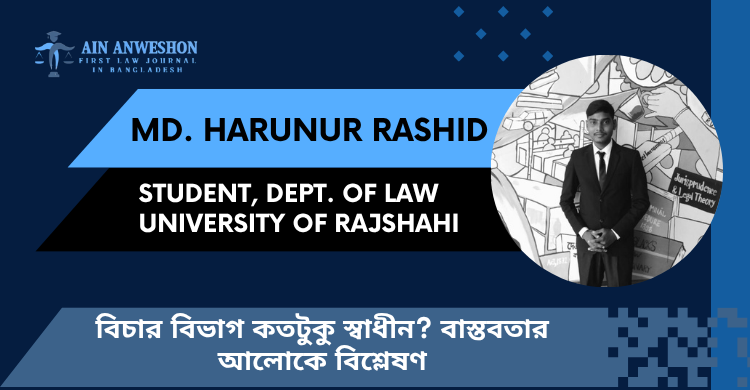জরুরি অবস্থা বলতে এমন সংকটজনক ও আকস্মিক অবস্থাকে বোঝায় যখন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে বলা যায়, জরুরি অবস্থা বলতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে কোনো আকস্মিক সংকটকালীন অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য কতিপয় মৌলিক অধিকারের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করাকে বোঝায়। সাধারণত যুদ্ধকালীন সময়, অভ্যন্তরীণ গোলযোগজনিত সময় বা অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সময় এ ধরনের জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।
অন্যদিকে, মৌলিক অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার থেকে নেওয়া কিছু অধিকারের সমষ্টি। মানবাধিকার হলো এমন কিছু স্বাভাবিক ও সার্বজনীন অধিকার, যা জন্মমাত্রই প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য—ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, জাতি, জাতীয়তা বা অন্য কোনো পার্থক্য বিবেচনা না করে।
মানবাধিকারের মধ্য থেকে যখন কতিপয় অধিকার কোনো একটি দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তা লঙ্ঘনের প্রতিকারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়, তখন সেগুলোকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। সংবিধানের মাধ্যমে এই অধিকারগুলো সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করা হয়, যাতে জনগণের স্বার্থ ও অধিকারগুলো সুরক্ষিত থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য মানুষের যেসব অধিকার রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত, তাদেরকে মৌলিক অধিকার বলে।
জরুরি অবস্থার বিধান অগণতান্ত্রিক কিছু নয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যে কোনো দেশের সংবিধানে বা আইনে এর বিধান রাখা যায়। রাষ্ট্র যদি টিকে থাকে তাহলে মৌলিক অধিকারসমূহও টিকে থাকবে, কিন্তু রাষ্ট্র যদি টিকে না থাকতে পারে তাহলে মৌলিক অধিকারও বিলুপ্ত হবে। সুতরাং, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে এমন সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে মৌলিক অধিকারগুলো যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তার জন্য জরুরি অবস্থার বিধান রাখা উচিত। লর্ড এটকিনসন R. v Halliday মামলায় বলেছিলেনঃ “নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা যতই মূল্যবান হোক না কেন, যুদ্ধ বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত জরুরি অবস্থায় উহা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কিছু অংশে খর্ব করা যায়।”
বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে জরুরি অবস্থার বিধান:
পাকিস্তান শাসনামলে জরুরি অবস্থার অহরহ অপব্যবহার দেখে ১৯৭২ সালের প্রথম সংবিধানে সংবিধান প্রণেতারা জরুরি অবস্থার বিধান রাখেননি। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের পর বছর পার হতে না হতেই দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে জরুরি অবস্থার বিধান সংবিধানে সংযোজন করা হয়।
জরুরি অবস্থা-সংক্রান্ত বিধান সংবিধানে সংযোজনের জন্য নতুন একটি ভাগ (নবম-ক) এবং উহাতে নতুন তিনটি অনুচ্ছেদ (১৪১ক, ১৪১খ, ১৪১গ) যোগ করা হয় এবং বর্তমান সংবিধানেও এই অনুচ্ছেদগুলো জরুরি অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।
সুতরাং এই অনুচ্ছেদগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৪১ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী “রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।” তবে ঘোষণার পূর্বে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।
১৪১খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণার সাথে সাথে ১৮ মৌলিক অধিকারের মধ্যে ৬টি মৌলিক অধিকার স্থগিত হয়ে যায়। ফলে এদের বলবৎকরণের কোনো প্রশ্ন থাকে না। বাকি থাকে ১২টি মৌলিক অধিকার। জরুরি অবস্থা চলাকালে এই ১২টি অধিকার বহাল থাকে। তবে ১৪১গ অনুযায়ী উক্ত ১২টি অধিকারের যে কোনোটির বা সবগুলোর বলবৎকরণের অধিকারকে রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে স্থগিত করে দিতে পারেন।
জরুরি অবস্থার বিধানের নেতিবাচক প্রভাব:
১. অধিকার স্থগিত করা:
জরুরি অবস্থা ঘোষণার সাথে সাথে সংবিধানের ১৪১খ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো স্থগিত হয়ে যায়। যতদিন জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকবে, ততদিন উক্ত অধিকারগুলোও স্থগিত থাকবে। এমনকি ১৪১গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা যে কোনো মৌলিক অধিকারের বলবৎকরণের অধিকার স্থগিত করতে পারেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে যতবারই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, প্রতিবারেই মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ এবং মৌলিক অধিকারের বলবৎকরণের অধিকার স্থগিত করা হয়েছিল, যা একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে কখনো কাম্য নয়।
২. নাগরিক স্বাধীনতা হ্রাস:
জরুরি অবস্থার সময় সরকার বাকস্বাধীনতা, মুক্ত গণমাধ্যম এবং সমাবেশের অধিকার সীমিত করতে পারে। যেমন ২০০৭ সালের জরুরি অবস্থায় রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
৩. গ্রেপ্তার ও হেফাজতের বিধান:
সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে গ্রেপ্তারের পর দ্রুত আদালতে হাজির করার অধিকার থাকলেও, জরুরি অবস্থার সময় এই অধিকার স্থগিত থাকে। ফলে Preventive Detention (আগাম গ্রেপ্তার)-এর সংখ্যা বেড়ে যায়, যা একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ।
৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হ্রাস:
জরুরি অবস্থার সময় সরকারের নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা বেড়ে যায়, যা বিচার বিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অনেক সময় আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।
৫. মানবাধিকার লঙ্ঘন:
জরুরি অবস্থায় নির্যাতন, বেআইনি গ্রেপ্তার, গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭-২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জরুরি অবস্থায় এই ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটেছিল।
৬. গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ:
গণমাধ্যম একটি রাষ্ট্রের পঞ্চম স্তম্ভ, যা নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য তুলে ধরে। কিন্তু জরুরি অবস্থার ফলে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে সেন্সরশিপের অধীনে আনা হয়। যেমন, ২০০৭ সালে “ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক অপারেশন আইন” ব্যবহার করে বিভিন্ন চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করা হয়।
সর্বোপরি বাংলাদেশের সংবিধানে জরুরি অবস্থার ঘোষণার ফলে নাগরিকদের উপর ইহার অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, এমনকি এমন সব মৌলিক অধিকারও স্থগিত করা হয়েছে, যেগুলোর সাথে জরুরি অবস্থার কোনো সরাসরি যোগ নেই।
বিগত সময়ের জরুরি অবস্থাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ সময়ই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এবং বিরোধী দলের মুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, যার ফলে সাধারণ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায় সংবিধানে বর্ণিত এই বিধান সরকারের জন্য ক্ষমতায় টিকে থাকার একটি অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।