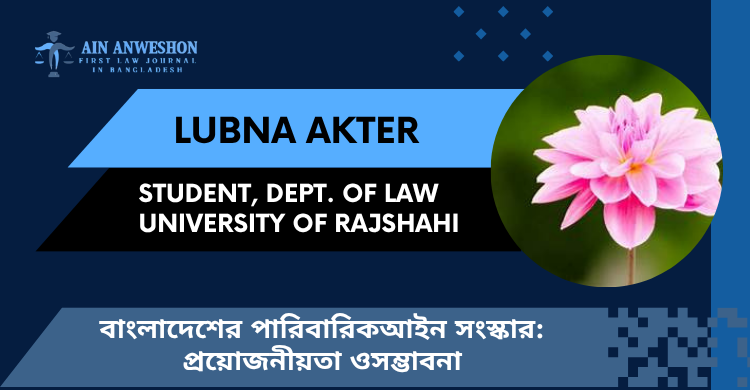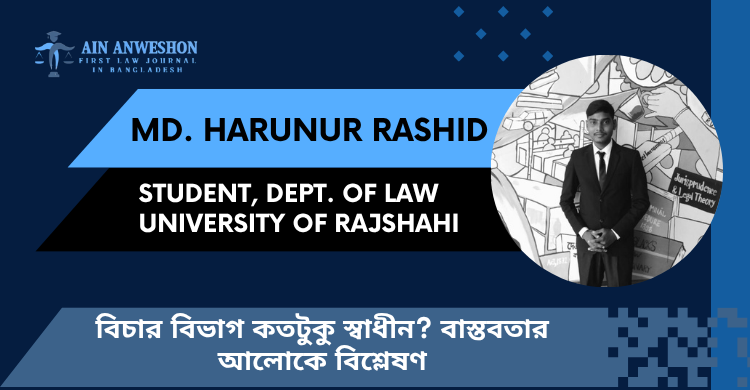একসময়, এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ভূখণ্ডে একটি ধারণার বীজ রোপিত হয়েছিল—একটি রাষ্ট্র যেখানে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারবে। বাংলাদেশ সেই আদর্শ নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আদর্শ ও রাজনৈতিক অভিলাষ প্রায়শই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতা দেশের সংবিধানে কখনো সুরক্ষিত হয়েছে, আবার কখনো তা দুর্বল হয়েছে। যে ধারণা একসময় সমঅধিকারের প্রতিশ্রুতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা এখন নানা রাজনৈতিক মতাদর্শের টানাপোড়েনে জর্জরিত। প্রশ্ন হলো—বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃতপক্ষে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, এবং এর ভবিষ্যৎ কোন পথে?
ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা নতুন কিছু নয় এবং এটি একান্তভাবেই পাশ্চাত্যের বিষয়ও নয়। যদিও ব্রিটিশ চিন্তাবিদ জর্জ জ্যাকব হলিওক প্রথম ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি প্রচলন করেন, রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণের চর্চা বহু পুরনো। মধ্যযুগে সম্রাট আকবরের ‘দীন-ই-ইলাহী’ নীতিতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যে প্রয়াস ছিল, তা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ। ইউরোপের দীর্ঘকালীন ধর্মীয় সংঘাতের পর ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণের ভিত্তি গড়ে তোলে। আধুনিক কালে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স এই নীতিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে, আর ভারত তা গ্রহণ করে ধর্মীয় বৈচিত্র্যের কারণে। কিন্তু বাংলাদেশে এই ধারণাটি কীভাবে প্রবেশ করল?
উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান বেশ জটিল। ব্রিটিশ শাসনকালে ধর্মীয় বিভেদকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, যার পরিণতিতে ১৯৪৭ সালের বিভাজন ঘটে। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ধর্মীয় সহনশীলতার পক্ষে ছিলেন। তবে সে আদর্শ বেশিদিন টিকে থাকেনি। পাকিস্তান ক্রমেই ইসলামী জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক দমন-পীড়ন পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনায় ধর্মীয় পরিচয়ের বদলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র পাকিস্তানি নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিল না; এটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তার বিরুদ্ধেও ছিল। তাই, ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু রাজনীতি কখনোই সরল রেখায় চলে না।
লালন, নজরুল, বাউল ও লোকসংগীতের ঐতিহ্যে ধর্মীয় সহাবস্থান ছিল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মূলধারার অংশ। ব্রিটিশ আমলে বাংলা রেনেসাঁস ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়শই ধর্মকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তাহলে প্রশ্ন আসে—ধর্মনিরপেক্ষতা কি কৃত্রিমভাবে আরোপিত, নাকি এটি বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত?
ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হওয়া উচিত, কারণ এটি সব নাগরিকের জন্য সমানাধিকার নিশ্চিত করে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাউকে ধর্মীয় কারণে বৈষম্যের শিকার হতে দেয় না। একই সঙ্গে এটি ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন রাষ্ট্রধর্ম ও রাজনীতি একসঙ্গে মিশে যায়, তখন সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। আধুনিক বিশ্বে অধিকাংশ সফল গণতান্ত্রিক দেশ ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে অনুসরণ করে। বাংলাদেশ যদি তার আন্তর্জাতিক অবস্থান দৃঢ় করতে চায়, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা অপরিহার্য।
ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলো বিষয়টির বিতর্কিত অবস্থান প্রমাণ করে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এটি ৮(১) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ১২ অনুচ্ছেদে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতা পরিস্থিতিকে বদলে দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসনের যাত্রা শুরু হয়, এবং ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে ‘আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর পথ সুগম হয়।
পরবর্তীতে, ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। তবে ২০১১ সালে ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ফিরিয়ে আনা হলেও, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বহাল রাখা হয়। এই সাংবিধানিক দ্বৈততা কি আদৌ সম্ভব? এই প্রশ্ন আজও বিতর্কিত।
ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। পক্ষের লোকেরা বলেন, এটি সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব কমায় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখে। বিপক্ষের লোকেরা মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবে প্রয়োগ করা কঠিন, বিশেষত যখন জনগণের একটি বড় অংশ ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতি সংবেদনশীল। কিন্তু ইতিহাস বলে—রাজনীতিতে ধর্মের উপস্থিতি বিভেদ সৃষ্টি করে।
বাংলাদেশ এখন এক দ্বিধার মাঝে দাঁড়িয়ে। একদিকে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যাবর্তন, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ধর্মের ব্যবহার। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা কি বাস্তবে রক্ষা করা হবে, নাকি ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিভাজন আরও অস্পষ্ট হয়ে যাবে? এই সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে ন্যায়বিচার, সাম্য ও গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির ওপর।
তথ্যসূত্র
জর্জ জ্যাকব হলিওক, ইংলিশ সেক্যুলারিজম: এ কনফেশন অফ বিলিফ (লন্ডন: জে. ওয়াটসন, ১৮৯৬)।
ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি (১৬৪৮)।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (গৃহীত ৪ নভেম্বর ১৯৭২, কার্যকর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২), যা ১৯৭৯ সালের পঞ্চম সংশোধনী, ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনী এবং ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে।
বাংলাদেশ ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিমিটেড বনাম বাংলাদেশ, (২০১০) ৬২ ডিএলআর (এডি) ২৯৮।
রাজীব ভার্গভ, দ্য প্রমিস অফ ইন্ডিয়াজ সেক্যুলারিজম (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০)।
ডোনাল্ড ই. স্মিথ, ইন্ডিয়া অ্যাজ অ্যা সেক্যুলার স্টেট (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩)।
ক্রিস্টোফ জাফ্রেলট, রিলিজিয়ন, কাস্ট অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া (কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১)।