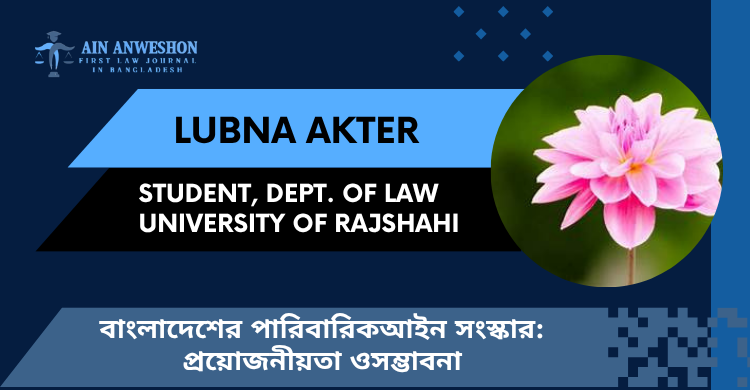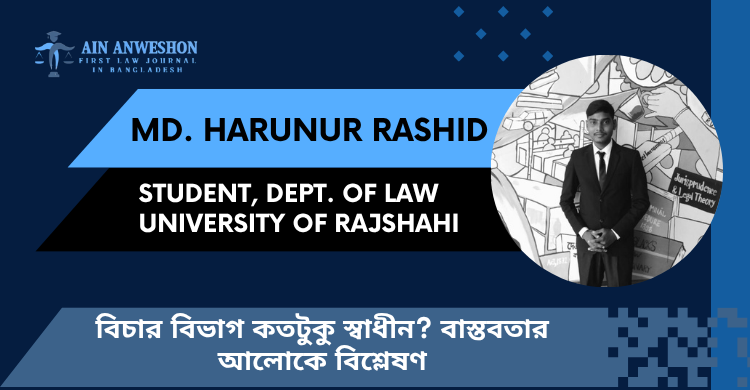বিশ্ব যখন প্রযুক্তির উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে উঠছে, তখন আইনি কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রমাণের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
বিশেষত সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে যেমন, হ্যাকিং, সাইবার বুলিং, জালিয়াতি এবং ডিজিটাল ডিভাইস বা তথ্য জড়িত অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে।
ডিজিটাল প্রমাণ বলতে সেই সকল তথ্যকে বোঝায় যা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার বা প্রেরণ করা যায় এবং যেটি অপরাধ তদন্তে তথ্য স্থাপন বা আইনি কার্যক্রমে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে: ডেটা ফাইল, নেটওয়ার্ক লগ, ই-মেইল, টেক্সট বার্তা, ডিজিটাল ছবি, অডিও এবং ব্রাউজিং হিস্ট্রি।
১. ডিজিটাল প্রমাণের ধরনসমূহ:
- ডিভাইস থেকে প্রাপ্ত তথ্য: কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ইউএসবি, হার্ডড্রাইভ ইত্যাদি থেকে পাওয়া তথ্য—যেমন: ফাইল, লগ, ব্রাউজিং হিস্ট্রি, ইমেইল, মাল্টিমিডিয়া।
- নেটওয়ার্ক লগ: ফায়ারওয়াল, রাউটার, সার্ভার ও ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম থেকে সংগৃহীত লগ, যা IP ঠিকানা, সময় ও কার্যক্রমের রেকর্ড রাখতে সাহায্য করে।
- সোশ্যাল মিডিয়া ও ম্যাসেজিং অ্যাপস: ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে, পোস্ট বা লিংকের মাধ্যমে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যায়।
- ওয়েবসাইটের তথ্য: অপরাধীদের নিয়ন্ত্রিত বা ভিজিট করা ওয়েবসাইটের রেজিস্ট্রেশন, ট্রাফিক লগ এবং ওয়েব-ভিত্তিক যোগাযোগের রেকর্ড।
- মেটাডেটা: ফাইলের ভিতরে লুকানো তথ্য, যেমন: তৈরির সময়, লেখকের নাম, অবস্থান ইত্যাদি, যা ঘটনার সময়কাল নির্ধারণে সহায়ক।
- ক্লাউড ডেটা: ড্রপবক্স, গুগল ড্রাইভ ইত্যাদিতে সংরক্ষিত তথ্য যথাযথ পরোয়ানার মাধ্যমে উদ্ধার করে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
২. বাংলাদেশে বিভিন্ন আইনের অধীনে ডিজিটাল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা:
বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রমাণের আইনি গ্রহণযোগ্যতা আইন ও বিধিমালার সমন্বয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতার জন্য কয়েকটি আইন প্রযোজ্য, যেমন:
● প্রমাণ আইন, ১৮৭২ (Evidence Act, 1872):
ধারা ৬৫বি (Section 65B): এই ধারা অনুযায়ী কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তৈরি নথি আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য, যদি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা হয়।
● তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (ICT Act, 2006):
ধারা ২(৪২): ‘ইলেকট্রনিক রেকর্ড’ এর সংজ্ঞা দেয় এবং এই ধরনের নথির আইনি বৈধতা নিশ্চিত করে।
ধারা ৬-৭, ১৬-১৭: ইলেকট্রনিক নথি, ডিজিটাল স্বাক্ষর ও নিরাপদ ইলেকট্রনিক রেকর্ডের আইনি স্বীকৃতি ও আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা করে।
● ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ইলেকট্রনিক লেনদেন আইন, ২০০০:
ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ও নথিকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে, যদি নির্ধারিত শর্ত পূরণ হয়।
এটি আইনি নথিতে ডিজিটাল স্বাক্ষরের বৈধতা নিশ্চিত করে।
● সাইবার অপরাধ (তদন্ত ও বিচার) আইন, ২০১৩:
ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া ও ডেটা লগসহ ইলেকট্রনিক প্রমাণ বৈধভাবে সংগৃহীত হলে তা আদালতে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়।
৩. প্রমাণ আইন অনুযায়ী ডিজিটাল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা:
বাংলাদেশের আইনি কাঠামো ডিজিটাল প্রমাণের গুরুত্ব স্বীকার করলেও, ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ৬৫খ ধারায় ইলেকট্রনিক রেকর্ডকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাগুলি বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে:
● প্রমাণীকরণ (Authentication):
ডিজিটাল প্রমাণ জমা দেওয়া পক্ষকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণটি সত্য ও অপরিবর্তিত। উদাহরণস্বরূপ, নথির উৎস, তৈরির তারিখ, ও ফাইলের অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে হবে।
● নির্ভরযোগ্যতা(Reliability):
ডিজিটাল প্রমাণ অবশ্যই মৌলিক, নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ফরেনসিক বিশ্লেষক দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে যে, তথ্যে কোনও হেরফের বা বিকৃত করা হয়নি।
● চেইন অব কাস্টডি (Chain of Custody):
ডিজিটাল প্রমাণের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য একটি স্পষ্ট হেফাজতের শৃঙ্খল বজায় রেখে পরিচালনা করতে হবে। প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে নথিবদ্ধ করতে হবে (কার মাধ্যমে সংগৃহীত, কোথায় সংরক্ষিত, কে ব্যবহার করেছে ইত্যাদি)।
● সনদপত্র (Certificate):
ইলেকট্রনিক রেকর্ড তৈরির জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামের নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যক্তির কাছ থেকে একটি সনদপত্রের প্রয়োজন হতে পারে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে প্রমাণটি খাঁটি এবং এটি স্বাভাবিক কার্যপ্রণালীর অংশ হিসেবে সংরক্ষণ বা তৈরি করা হয়েছিল।
৪. ICT Act অনুযায়ী ডিজিটাল প্রমাণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ:
● ধারা ৬ – ইলেকট্রনিক রেকর্ডের আইনি স্বীকৃতি:
এই ধারায় বলা হয়েছে যে, ইলেকট্রনিক রেকর্ডগুলি লিখিত নথির সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে, যদি সেগুলি ইলেকট্রনিক আকারে তৈরি, সংরক্ষণ বা পাঠানো হয়।
এটি নিশ্চিত করে যে ডিজিটালভাবে তৈরি চুক্তি, চুক্তি বা রেকর্ডগুলির আইনি অবস্থান কাগজের নথির মতোই।
● ধারা ৭ – ডিজিটাল স্বাক্ষরের আইনি স্বীকৃতি:
এই ধারাটি ইলেকট্রনিক রেকর্ডের প্রমাণীকরণের জন্য ব্যবহৃত ডিজিটাল স্বাক্ষরকে আইনি স্বীকৃতি দেয়।
এটি নিশ্চিত করে যে যদি কোনও আইনে কোনও স্বাক্ষর বা নথির প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হয়, তবে নির্ধারিত মান পূরণকারী একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর সেই প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে।
● ধারা ১৬ – নিরাপদ ইলেকট্রনিক রেকর্ড:
যদি কোন ইলেকট্রনিক রেকর্ডকে “নিরাপদ” (যেমন, এনক্রিপ্ট করা, টাইম-স্ট্যাম্পড, টেম্পারিং থেকে সুরক্ষিত) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তাহলে আদালত ধরে নিতে পারে যে এটি সত্য এবং এটি পরিবর্তন করা হয়নি।
এটি ডিজিটালি সুরক্ষিত রেকর্ডের সাক্ষ্যগত মূল্যকে শক্তিশালী করে।
● ধারা ১৭ – নিরাপদ ডিজিটাল স্বাক্ষর:
যদি কোনও সুরক্ষিত প্রক্রিয়া (যেমন ক্রিপ্টোগ্রাফি ) ব্যবহার করে একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর তৈরি করা হয়, তাহলে আদালত ধরে নিতে পারে যে এটি বৈধ এবং স্বাক্ষরকারীর।
এটি আদালতের কার্যক্রমে ইলেকট্রনিক নথির প্রমাণীকরণে সহায়তা করে।
● ইলেকট্রনিক বার্তা সম্পর্কিত:
আদালত ধরে নিতে পারে যে, একটি ইলেকট্রনিক বার্তা (যেমন, ইমেল বা এসএমএস) সেই ব্যক্তি দ্বারা পাঠানো হয়েছে যার নাম প্রেরক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি না অন্যথায় প্রমাণিত হয়।
যদি না জালিয়াতি বা প্রতারণার প্রমাণ থাকে, তাহলে ইলেকট্রনিক বার্তাগুলিকে ডিজিটাল প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হবে।
৫. বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতায় চ্যালেঞ্জসমূহ:
● সহজ পরিবর্তনযোগ্যতা:
ডিজিটাল প্রমাণ সহজেই পরিবর্তন, মুছে ফেলা বা দূষিত করা যেতে পারে, হয় ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে।
ডিজিটাল প্রমাণ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়, কারণ যেকোনো পরিবর্তন বা পরিবর্তন প্রমাণকে আদালতে অগ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে।
● প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব:
ডিজিটাল প্রমাণ গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি হল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, তদন্তকারী এবং এমনকি বিচারকদের মধ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব।
ডিজিটাল ফরেনসিকের জন্য বিশেষ জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, এবং ডিজিটাল প্রমাণ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ এবং প্রমাণীকরণ করতে পারে এমন বিশেষজ্ঞদের ছাড়া, অনুপযুক্ত পরিচালনা এবং ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি থাকে।
● চেইন অব কাস্টডির দুর্বলতা:
ডিজিটাল প্রমাণ পরিবর্তন বা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। প্রমাণ পরিচালনা এবং সংরক্ষণের জন্য নথিভুক্ত করার জন্য একটি সঠিক হেফাজতের শৃঙ্খল বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
প্রমাণ সংগৃহীত ও সংরক্ষণের সময় সঠিক নথিভুক্তি না হওয়ায় আদালতে সেটির সত্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।
● এনক্রিপশন ও গোপনীয়তা সমস্যা:
এনক্রিপশন প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সাথে সাথে, অনেক ডিজিটাল ডিভাইস এবং যোগাযোগ নিরাপদ এবং সঠিক ডিক্রিপশন কী ছাড়া অ্যাক্সেস করা কঠিন।
বাংলাদেশের তদন্তকারীরা এনক্রিপ্ট করা প্রমাণ নিয়ে কাজ করার সময় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন, বিশেষ করে যদি তাদের কাছে এটি ডিক্রিপ্ট করার প্রযুক্তিগত উপায় না থাকে অথবা গোপনীয়তা আইন এই তথ্য অ্যাক্সেসকে জটিল করে তোলে।
● আইনি প্রটোকল অনুসরণে ঘাটতি:
ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি প্রোটোকল অনুসরণ করতে হবে।
প্রমাণ সংগ্রহ ও উপস্থাপনে আইনি প্রক্রিয়া না মানলে, আদালত সেটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।
● সীমান্ত পেরিয়ে তথ্য সংগ্রহের সমস্যা:
যেহেতু সাইবার অপরাধ প্রায়শই সীমান্তের বাইরের কার্যকলাপ জড়িত থাকে, তাই বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সার্ভারগুলিতে সংরক্ষিত প্রমাণ সংগ্রহে আইনি জটিলতা দেখা দেয়।
৬. উপসংহার:
বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা একটি দৃঢ় আইনি কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে প্রমাণ আইন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর আইন। তবে, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, হেফাজতের শৃঙ্খল, এনক্রিপশন এবং গোপনীয়তা আইন সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি এর অখণ্ডতা এবং গ্রহণযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে।