বাংলাদেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থা: সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ বা আইনসভা হলো এমন একটি আইনসভা যা দুটি পৃথক কক্ষ নিয়ে গঠিত। যেখানে একটি কক্ষকে “উচ্চকক্ষ”; অন্যটিকে “নিম্নকক্ষ” বলা হয়। এই ধরনের আইনসভায় আইন প্রণয়নে সমান ক্ষমতার ভারসাম্য বা “চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স” নিশ্চিত করা হয়। এই ধরনের আইনসভায় নিম্নকক্ষের সদস্যরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। তাদের হাতেই থাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। তবে আইন কার্যকর […]
বাংলাদেশের পারিবারিক আইন সংস্কার: প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা
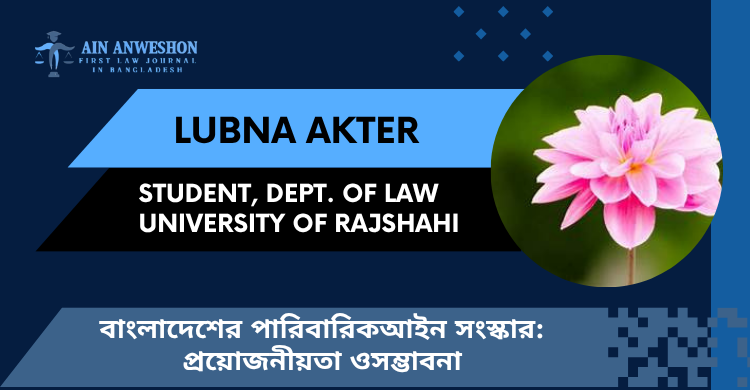
ভূমিকা: বাংলাদেশের পারিবারিক আইন সমাজের মৌলিক ভিত্তি, যা ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্ক এবং পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করতে ব্যবহৃত হয়। তবে, এই আইনে নারীর অধিকার, ধর্মীয় বিধান, সামাজিক বাস্তবতা এবং সংস্কৃতির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। এসব কারণে, অনেক ক্ষেত্রে আইনি অধিকার ও সমতা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবেদনে, বাংলাদেশের পারিবারিক আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং তার সম্ভাবনা […]
বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা: একটি আইনি ও ব্যবহারিক বিশ্লেষণ

ভূমিকাভোক্তা অধিকার সুরক্ষা একটি সুশৃঙ্খল ও ন্যায়সঙ্গত বাজারব্যবস্থা গঠনের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে ভোক্তারা প্রায়ই নিম্নমানের পণ্য, অতিরিক্ত মূল্য, প্রতারণা এবং সঠিক তথ্যের অভাবে ভোগান্তির শিকার হন। ২০০৯ সালের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন পাস হওয়ার পর কিছু অগ্রগতি হয়েছে, তবে বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে এখনও অনেক সমস্যার সমাধান হয়নি।এই গবেষণায় বাংলাদেশের ভোক্তা […]
সমসাময়িক পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক আইনের সীমাবদ্ধতা এবং তা থেকে পরিত্রানের উপায়

ভূমিকা: জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ বিপ্লবের এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এসে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিরাজ করছে। যে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সকলে ওয়াকিবহাল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে আমরা ভেবেছিলাম যে দেশে একটি বিপ্লবের সূচনা হবে। সেটা তো হলই না, এমনকি কোন সংস্কারও এখনো পর্যন্ত কার্যকর হলো না। এছাড়া দেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছে। যার সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ সমাজের সেচ্ছাচারিতা করছে। চাঁদাবাজ, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, খুন, গুম ইত্যাদি এখনকার নিত্যদিনের ঘটনা। এর মূল কারণ দেশের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, দুর্বল আইন, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাব, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দুর্বলতা, স্থানীয় সরকারি কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়া, বৃহত্তর রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বয়ের ব্যাপক প্রভাব ইত্যাদি। এতক্ষণ সমস্যাময়িক বর্ণনা করলাম। এখন আমরা দেখব সমসাময়িক পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক আইনের সীমাবদ্ধতা ও এর থেকে পরিত্রাণের উপায়। ✔(১.) সাংবিধানিক আইনের সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে গৃহীত হলেও, এর বিভিন্ন বিধান এবং পরবর্তী সংশোধনীগুলো সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কিছু সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: ◑ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সমস্যা: সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী এবং কার্যনির্বাহী বিভাগের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। উদাহরণস্বরূপ, সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা সীমিত করা হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা এবং স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে। প্রভাব: এটি ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক প্রভাব এবং সংসদের স্বাধীনতা হ্রাসের কারণ হতে পারে। এ আইনটি সংস্কার করে সংবিধানে ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংসদ সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ অসম্ভবপর। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ◑নির্বাচনী ব্যবস্থার দুর্বলতা সমস্যা: সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলেও, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে এর কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থাৎ ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক এবং জনগণের আস্থার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। প্রভাব: এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। ◑ প্রতিরোধমূলক আটক এবং মানবাধিকার সমস্যা: সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদ প্রতিরোধমূলক আটকের বিধান রাখে, যা বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। এই আইন বিচার ছাড়া আটকের সুযোগ দেয়, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের কারণ হয়েছে। প্রভাব: এটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই কালো আইনকে কাজে লাগিয়ে তথাকথিত স্বৈরাচার ‘আয়না ঘর’ এর মতো জঘন্য এবং আইন বিরোধী একটি সেল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ◑ সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়ার জটিলতা সমস্যা: সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে সংশোধনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন, যা রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবে কঠিন। প্রভাব: জরুরি সংস্কার বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে, যা সংবিধানকে সমসাময়িক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে বাধা সৃষ্টি করে। ◑ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সীমাবদ্ধতা সমস্যা: সংবিধানে সামাজিক সমতা, নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং মানবাধিকারের কথা বলা হলেও, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নারীর প্রতি সহিংসতা, শিশুশ্রম এবং দুর্নীতির মতো সমস্যা মোকাবিলায় সাংবিধানিক বিধান কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয় না। প্রভাব: এটি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতা প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে। ✔(২.) সমাধানের উপায় সাংবিধানিক আইনের সীমাবদ্ধতা দূর করতে এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে: ক. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাব: সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা। এছাড়া, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা। ফলাফল: এটি ক্ষমতার অপব্যবহার কমাবে এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা বাড়াবে। খ. নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তাব: নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করতে সাংবিধানিক সংস্কার এবং নিরপেক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রবর্তন। এছাড়া, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ইলেকট্রনিক ভোটিং এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা। Separation of power নিশ্চিত করতে হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনে সংসদ সদস্য বা রাষ্ট্রপতির কোন হাত থাকবে না। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত করা যেতে পারে। ফলাফল: জনগণের আস্থা ফিরবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে। ◑ মানবাধিকার সুরক্ষা প্রস্তাব: সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদ এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন সংশোধন করে প্রতিরোধমূলক আটকের বিধান সীমিত করা। স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন এবং বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। ফলাফল: মানবাধিকার লঙ্ঘন কমবে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ◑ সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাব: সাম্প্রতিক জুলাই বিপ্লবের পর অধ্যাপক আলী রিয়াজের নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন। এর মধ্যে রয়েছে নতুন সংবিধান প্রণয়ন, নাগরিকতন্ত্র প্রবর্তন এবং মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। […]
বাংলাদেশে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব: মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা

ভূমিকা বাংলাদেশে মাদকাসক্তি একটি গুরুতর সামাজিক ও আইনগত সমস্যা, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(২) অনুচ্ছেদে মাদকের ব্যবহার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। ক্রমবর্ধমান মাদক সমস্যা মোকাবিলায় সরকার ২০১৮ সালে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে, যার লক্ষ্য ছিল মাদকাসক্তি ও মাদক পাচার প্রতিরোধ করা। এই প্রবন্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আইনি কাঠামো: মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (NCA 2018) মাদকের বিরুদ্ধে আইনগত কাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। এটি ১৯৯০ সালের মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনকে বাতিল করে এবং কঠোর শাস্তি, উন্নত আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়া এবং মাদকদ্রব্যের ব্যাপক সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করে। আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: কঠোর শাস্তি: ২০০ গ্রাম বা তার বেশি হেরোইন, কোকেন বা ইয়াবার মতো মাদক উৎপাদন, বিতরণ বা পাচারে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। নিয়ন্ত্রিত মাদকের তালিকা সম্প্রসারণ: পূর্ববর্তী আইনে উল্লেখ না থাকা নতুন সিন্থেটিক মাদক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রিকিউরসার কেমিক্যালের নিয়ন্ত্রণ: মাদক তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের ব্যবহার ও বাণিজ্যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও অর্থপাচার প্রতিরোধ: মাদক পাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন কর্মসূচি: শুধু শাস্তি নয়, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮–এর কার্যকারিতা আইনটি প্রণয়নের পর বাংলাদেশের মাদক নিয়ন্ত্রণে কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে: ১. মাদক জব্দ ও গ্রেফতার বৃদ্ধি: আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে, যার ফলে মাদক জব্দ ও পাচারকারীদের গ্রেফতার বেড়েছে। ২. প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত শক্তিশালীকরণ: মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (DNC) কার্যক্রম জোরদার ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩. জনসচেতনতা কার্যক্রম: সরকার ও বিভিন্ন এনজিও মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে যৌথভাবে আন্তঃদেশীয় মাদক পাচার প্রতিরোধে কাজ করছে। সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে: ১. আইন প্রয়োগে অতিরিক্ত নির্ভরতা: আইনটি মাদকের সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ যেমন বেকারত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় খুব একটা কার্যকর নয়। ২. বিচারিক বিলম্ব ও দুর্নীতি: মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ আইনের বাস্তবায়ন দুর্বল করেছে। ৩. পুনর্বাসন কেন্দ্রের অভাব: […]
বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধূমপান: কারণ, প্রভাব এবং প্রতিরোধ

বাংলাদেশে ধূমপান একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা, যেখানে তামাকের বাজার বিশাল এবং তামাকজনিত অসুস্থতার উচ্চ হার রয়েছে। ধূমপান মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী হুমকি। বাংলাদেশও এর একটি অংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধূমপানের হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ‘গ্লোবাল অ্যাকশন টু এন্ড স্মোকিং’ অনুসারে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী […]
বিচার বিভাগ কতটুকু স্বাধীন? বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ
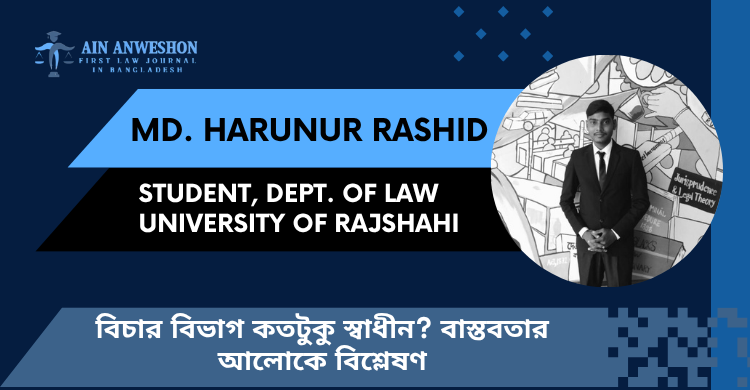
বাংলাদেশের বিচার বিভাগ একটি স্বাধীন ও সমান্তরাল শাখা হিসেবে গণ্য হলেও এর প্রকৃত স্বাধীনতা এবং কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংবিধানিক এবং সামাজিক প্রভাব বিদ্যমান। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একটি সুসংগঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তবে বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেকটা সংকুচিত এবং বিতর্কিত, যা বিশেষত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং প্রশাসনিক চাপে প্রকাশ পায়। বিচার বিভাগের সাংবিধানিক অবস্থান: […]
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আদালত প্রাঙ্গণের প্রবেশযোগ্যতা : সমান প্রবেশাধিকারের জন্য আইনি সংস্কার ও মূল্যায়ন

প্রস্তাবনা: শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি মৌলিক অধিকার হল বিচার পাওয়ার অধিকার। তবে, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশে এখনও অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে। পরিকাঠামোগত বাধা, আইনগত সীমাবদ্ধতা এবং প্রশাসনিক অবহেলার কারণে তারা তাদের বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই প্রবন্ধে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতার সমস্যা, বিদ্যমান আইন এবং আইনি ও পরিকাঠামোগত […]
পিতামাতার ভরনপোষণ আইন ২০১৩: বিশ্লেষণ ও সীমাবদ্ধতা।

পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণ আইন, ২০১৩, বাংলাদেশে বাচ্চাদের তাদের বয়স্ক পিতামাতার যত্ন নেওয়ার জন্য আইনত বাধ্যতামূলক করার জন্য চালু করা হয়েছিল। এই আইনটি তাদের পিতামাতাকে আর্থিক, সংবেদনশীল এবং শারীরিক সহায়তা প্রদানের জন্য শিশুদের দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয়। এটি খাদ্য, পোশাক, চিকিত্সা যত্ন, আবাসন এবং সাহচর্য সহ রক্ষণাবেক্ষণকে সংজ্ঞায়িত করে, এটি নিশ্চিত করে যে পিতামাতারা তাদের বৃদ্ধ বয়সে পরিত্যক্ত […]
সাইবারস্পেসে বিচারব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সমাধান

ভূমিকা : বর্তমান যুগ ইন্টারনেটের যুগ। আমরা এখন ডিজিটাল যুগে বাস করছি। ডিজিটাল যুগ মূলত ইন্টারনেট ও বিশ্বব্যাপী ওয়েবের (World Wide Web) প্রসারকে বোঝায়। এটিকে সাইবারস্পেস নামেও আখ্যায়িত করা হয়। সাইবারস্পেস (Cyberspace) ঐতিহ্যগত ভৌগোলিক সীমানার বাইরে পরিচালিত হয়, যা বিচারব্যবস্থার জন্য জটিলতা সৃষ্টি করে। এই সীমাহীন পরিবেশে দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করতে বিভিন্ন দেশের আইন কীভাবে অনলাইন […]

