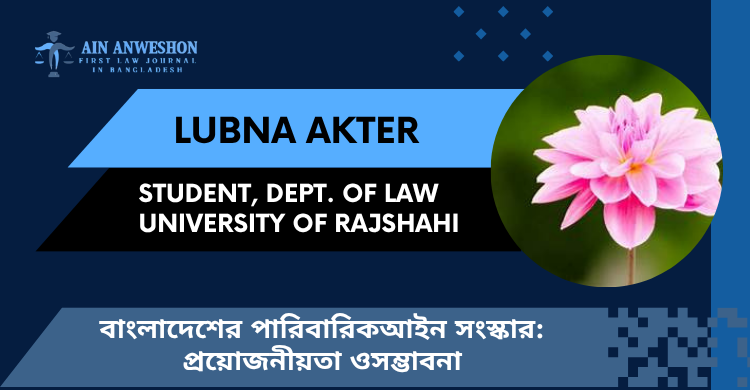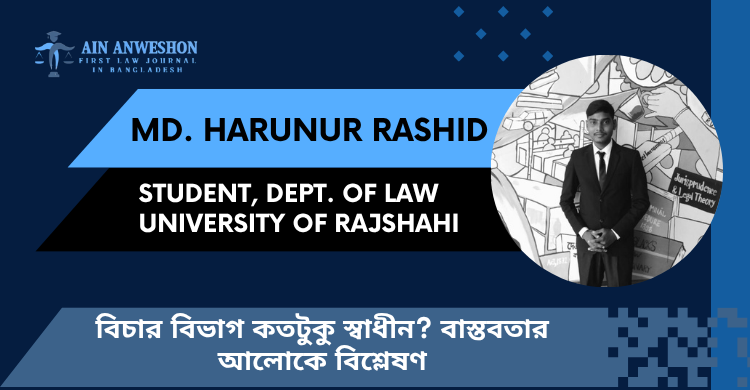সিভিল মামলায় জট : বাংলাদেশের সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলাগুলোর একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ
ভূমিকা
বাংলাদেশের আইন ও বিচারব্যবস্থা কমন ল আইনব্যবস্থায় গড়ে উঠেছে যা ঔপনিবেশিক আমলের দান। ব্রিটেনের প্রায় ২০০ বছরের শাসন আমলে ছিল ভারতবর্ষ। সেই সময়ে ১৭৭০-১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে পর্যায়ক্রমে বিচারিক সিদ্ধান্তের ওপর তৈরি হওয়া ব্রিটিশ আইন সরাসরি এবং ঔপনিবেশিক আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে মোটামুটি সবই ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা হয়েছে। বিচার পদ্ধতি, পুলিশ পদ্ধতি, অপরাধ আইন, দেওয়ানি আইন, চুক্তিগত আইন সহ মৌলিক আইনসমূহের সবকিছুই কমন ল এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখন পর্যন্ত আইনগুলো সামান্য সংশোধিত বা বিশেষ আইন তৈরি হলেও মৌলিক বিষয়গুলো ২৫০ বছরে আজও বহাল আছে। অপরদিকে উপমহাদেশের কমন ‘ল’ ব্যবস্থার দেশ ভারতে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে।
সম্প্রতি পাকিস্তানে দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধন হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ, জনসংখ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও আইনগুলো আমরা অনুসরণ করে চলেছি যা এককথায় সেকেলে এবং আমাদের আধুনিক বিচারব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে বললে ভুল হবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো স্বয়ং বৃটেনে ২৫০ বছরে বহুল পরিবর্তন হয়েছে বিচারব্যবস্থায় ও আইনসমূহে কিন্তু আমরা এখনো সেগুলো ব্যবহার করে চলেছি।
মামলাজট
মামলাজট আসলে কি? মামলা জট কেনো বলছি বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরা যাক। কমন ল বিচার ব্যবস্থার দেশগুলোতে এই পরিভাষাটি ব্যাপক ব্যবহৃত। মামলাজট বলতে আসলে বোঝায় নির্দিষ্ট সময় সীমার চেয়ে বেশি সময় ধরে আদালতে বিচারাধীন থাকা মামলাসমূহ। এই সময় সীমা কখনো নির্দেশনামূলক মাত্র। যেমন সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার। এটি আবার কখনো কখনো বাধ্যতামূলক যেমন বিশেষ আইনসমূহ বা বিশেষ আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহের বিচার যা সাধারণত ট্রাইব্যুন্যালে সম্পন্ন হয়। দেওয়ানি বিষয়ক মামলার ক্ষেত্রে উদাহরণ অর্থঋণ আদালত। কিন্তু মামলা নিষ্পত্তিতে বিশেষ বিধান থাকার পরেও অনেক ক্ষেত্রে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না।
মামলাজটের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। কারণগুলিকে কয়েকটি বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। ক) আইনগত বা টেকনিক্যাল কারণ খ) পলেসি বা নীতিনির্ধারণ জনিত কারণ গ) সামাজিক ও অন্যান্য কারণ।
ক) আইনগত বা টেকনিক্যাল কারণ
দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮ এর ক্রটিসমূহ যা মামলা জটে সরাসরি দায়ী:
১) সমন ও নোটিশ জারিতে বিলম্ব
আদি এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানি আদালতসমূহে মামলা দায়েরের পরবর্তী পর্যায়ে মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি বিলম্বিত হয় মামলার সমন ও নোটিশ জারিতে অস্বাভাবিক সময় ব্যয়ের জন্য। মূলতঃ যথারীতি সমন জারি দেওয়ানি মামলার গতিশীলতার পূর্বশর্ত হলেও দেশের আদালতসমূহে সমন জারিতে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে কোনো একটি দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়েরের পর ক্ষেত্রবিশেষে, শুধু এই কারণেই কয়েক বছরের দীর্ঘসূত্রিতার সূত্রপাত ঘটে।
শতবর্ষী বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সমন সংক্রান্ত বিধান কিছুটা সংশোধন হলেও মৌলিক বিষয়গুলো একই রয়েছ পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব বিভিন্ন জেলায় সমন জারিতে বিলম্ব ইত্যাদি কারণে মামলার প্রাথমিক পর্যায়েই দীর্ঘসূত্রতায় আটকে যায়।
২) লিখিত জবাব দাখিলে বিলম্ব
সমন/নোটিশ জারিতে অস্বাভাবিক বিলম্বের পরেই মামলার পরবর্তী পর্যায় তথা জবাব দাখিলে বিবাদী/প্রতিপক্ষের বিলম্বের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রায়ই দেখা যায় মামলার বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিলের জন্য পুনঃপুনঃ সময় নেয় যার মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায় যা মামলাজট বৃদ্ধিতে অন্যতম কারণ।
৩) টাইম পিটিশন
এক মামলা চলমান থাকা অবস্থায় প্রত্যেক শুনানিতে আইনজীবীর সময় চাওয়া তথা টাইম পিটিশন চাওয়ার কোনো সীমা নেই। একটি মামলার তারিখ আাসার পর বাদী বা বিবাদীপক্ষের আইনজীবী শুনানি না করে সময় চাইতে পারেন এবং আদালত সাধারণত সময় দিয়ে থাকেন। একটি মামলা শুনানি হওয়ার দিনে শুনানি না করলে কমপক্ষে ২ মাস পর আবার আরেকটি তারিখ আসতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় মামলা চালানোর প্রস্তুতির অভাবে, মামলা হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় নিছক টাইম পিটিশন করা হয় যা একটি স্বাভাবিক মামলাকে কমপক্ষে ২-৩ বছর পিছিয়ে দিতে পারে।
৪) বাদীপক্ষ কর্তৃক পুনঃপুনঃ আরজি সংশোধন
মামলার পর বাদীপক্ষ কর্তৃক পুনঃপুনঃ আরজি সংশোধন মামলার বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অনেক সময়েই বাদীপক্ষ মামলার প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি ব্যতিরেকে অথবা অপ্রতুল দলিলাদি নিয়ে মামলা দায়ের করে থাকে। জরুরি প্রয়োজনে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বাদীপক্ষকে পরবর্তীতে আরজি সংশোধনের দরখাস্ত করতে হয় এবং মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে এসব দরখাস্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয়। আবার এ ধরনের দরখাস্ত পুনঃ পুনঃ দাখিল ও মঞ্জুর হলে অনেক ক্ষেত্রেই নতুন করে তদবির গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিংবা অনেকক্ষেত্রে বিবাদীপক্ষকে অতিরিক্ত জবাব দাখিলের সুযোগ দিতে হয়। যার ফলে সামগ্রিকভাবে মামলার বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতে বাধ্য।
৫. ছানি মামলা
কোনো দেওয়ানি মামলায় বাদী গরহাজির থাকায় মামলা খারিজ হলে কিংবা বিবাদী গরহাজির থাকায় মামলা একতরফা শুনানি হলে আদালতের সেই খারিজ আদেশ বা একতরফা আদেশের রহিত করতে যে মামলা করা হয় তার নাম ছানি মামলা। একটি মামলার এতরফা শুনানি এবং ডিক্রি প্রদান করা হয় বাদী বা বিবাদীর অনুপস্থিতিতে যা প্রদান করা হয় নির্দিষ্ট গ্রাউন্ডসে কিন্তু আইন বলছে অনুপস্থিত বাদী/বিবাদী পুনরায় কারণ দেখিয়ে একতরফা ডিক্রি বা জারি ডিক্রি বাতিলের আবেদন করতে পারে কিংবা মূল মামলায় ফেরত আসতে পারে। ফলে পুনরায় একটি মামলা নতুন করে দুই তরফা শুনানি শুরু হয় আর মাঝখানে কেটে যায় বছরের পর বছর। এ ধরনের সানি মামলা বাংলাদেশে ব্যাপক পরিমাণে করা হয়।
আবার দেখা যায় একতরফা ডিক্রি বাতিলের আবেদন, আপিল ও ছানি মামলার তমাদি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিনিধিত্ব মামলায় একই সাবজেক্ট ম্যাটারে নতুন কোনো ইস্যুতে আপিল দায়ের করে মূল মামলায় ফেরত যাওয়ার আবেদন করা হয় এবং আদালত তা মঞ্জুর করেন; ফলে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত হতে থাকে একটি মামলা।
৬) অন্তবর্তীকালীন দরখাস্ত দাখিলের প্রবণতায় মামলাজট
এছাড়া মামলা চলাকালীন অন্তর্বর্তীকালীন প্রদত্ত আদেশ অনেকক্ষেত্রেই মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন আদালতে মামলার বিচার চলাকালে এরূপ অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্ত ও আদেশ যেভাবে মামলার বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে তার কয়েকটি নমুনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে:
(১) মামলার বিচার পর্যায়ে discovery inspection, injunction এর দরখাস্ত আনয়ন
(২) এডভোকেট কমিশনের নিয়োগে বিলম্ব
(৩) পুনঃপুনঃ কমিশনের দরখাস্ত আনয়ন ও কমিশনার নিয়োগ
(৪) কমিশন রিপোর্ট দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্ব এবং প্রায়শঃই রিপোর্টের উপর আপত্তি প্রদান।
আবার অনেক ক্ষেত্রে এ ধরণের দরখাস্তসমূহের ওপর আদেশ প্রদান করা হলে তার বিরুদ্ধে রিভিশন দাখিল করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষ উক্ত রিভিশনসমূহ নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়, ফলে সামগ্রিকভাবে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।
৭) সাক্ষ্য উপস্থাপনে অনীহা
দেশের বিভিন্ন জজশিপের বিচারকবৃন্দের সহিত আলোচনা ও মামলার পরিসংখ্যানে মামলার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক সাক্ষ্য উপস্থাপনে অনীহার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত হয়। এ ব্যাপারে সকল আইনজীবীর অফিস অধিকতর সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করা প্রয়োজন তাছাড়া দ্রুত মামলা নিস্পত্তি সম্ভবপর নয়।
০৮) এজলাস সংকট
দেশের প্রতিটি উপজেলার জন্য একটি করে আদি এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানি আদালত থাকলেও জেলা জজ আদালতসমূহে সমসংখ্যক এজলাস কক্ষ নেই। যার ফলে প্রায় সব জাজশিপেই একাধিক বিচারককে একই এজলাস ও খাস কামরা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়। অনেক জাজশীপে জেলা জজ আদালত পরিদর্শনকালে এজলাস ভাগাভাগির বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। একই এজলাস একাধিক বিচারক কর্তৃক ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার ফলে একজন বিচারকের একটি কর্মদিনের মোট কর্মঘণ্টা বিভাজ্য হয়ে যায়। যার ফলে সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচারাধীন মামলার শুনানীতে যে সময় ব্যয় করা প্রয়োজন, তা ব্যয় করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া এতে কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়, কাজের স্পৃহা নষ্ট হয়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সাক্ষ্যগ্রহণ সম্ভবপর হয়।
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অধস্তন নিম্ন আদলতসমূহের মৌলিক তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। অধস্তন আদালতসমূহ The civil courts Act 1887,Code of Civil procedure 1908, এবং Code of Criminal Procedure 1898, The evidence Act 1872 অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। দেওয়ানি বিষয়গুলোর আদালতকে জেলা জজ এবং নিম্নে সহকারী জজ ও সিনিয়র সহকারী জজ। ফৌজদারি বিষয়সমূহের আদালতকে দায়রা আদালত এবং নিম্নে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত রয়েছে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহ গঠন ও কার্যাবলি আলাদা হলেও আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার ৫০ বছরেও একই বিচারকগণ একই সাথে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলার বিচার করে আসছেন।
আলাদা এজলাস বা কোর্ট নয় বরং যখন একজন জজ ক্রিমিনাল মামলার বিচার করেন তখন তিনি দায়রা জজ এবং আদালতের নাম দায়রা জজ আদালত আবার যখন একজন বিচারক দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করেন তখন তাকে বলা হয় জেলা জজ এবং আদালতের নাম জেলা জজ আদালত।
একই বিষয় যুগ্ম এবং অতিরিক্ত জেলা/দায়রা জজদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে বর্তমানে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট নির্বাহি বিভাগ হতে আলাদা হওয়ার ফলে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ একই সাথে দেওয়ানি মামলার বিচার করেন না বা সহকারী বা সিনিয়র সহকারী জজগণ দেওয়ানি বিষয়সমূহের সাথে সাথে একই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেসি না করলেও বিচারিক পদন্নোতিতে রদবদল করে ক্রিমিনাল এবং দেওয়ানি দুই বিষয়েই বিচার করানো হয় এবং দক্ষতা বাড়ানো হয়। এমনকি পরবর্তীতে বিশেষ আইনের অধীনে দ্রুত বিচার নিশ্চিতে প্রতিস্থাপিত ট্রাইবুন্যালগুলিও একই জেলা জজ বা দায়রা /অতিরিক্ত/যুগ্ম জজ বিচারকগণকে দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে! একই বিচারক কর্তৃক একাধিক বিষয়ে বিভিন্ন আদালত পরিচালনা করায় যথেষ্ট সময়ে একটি মামলার সমাধান আসা অনেক কঠিন। যার ফলে মামলাজটে তা অন্যতম একটি কারণ।
বিশদভাবে বিশ্লেষণে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় দেওয়ানি আদালতসমূহে দেওয়ানি মামলা বিচারের।
ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার কারণসমূহ এবং তা রোধে পর্যালোচনা নিম্নরূপ।
১। সমন ও নোটিশ জারীতে বিলম্ব:
আনি এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানী আদালতসমূহে মামলা দায়েরের পরবর্তী পর্যায়ে মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী সময় বিলম্বিত হয় মামলার সমন ও নোটিশ জারীতে। ক্ষেত্রবিশেষে, শুধু এই কারণেই মামলা নিষ্পত্তিতে কয়েক বছরের দীর্ঘসূত্রিতার সূত্রপাত ঘটে।
তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে বাদীপক্ষ কর্তৃক সমনে বিবাদীর ভুল নাম কিংবা ভুল ঠিকানা প্রদান করা হয়, বিধায় ঐ ত্রুটিপূর্ণ সমন জারী সম্ভবপর হয় না। যার ফলে সম্পূর্ণ মামলাটির বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়।
মূলত দুইশত বছরের পুরোনো সমন জারী সংক্রান্ত পদ্ধতি এবং প্রতি বছর বিপুল পরিমান দায়েরকৃত মামলার বিপরীতে সমন জারীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল না থাকায়, সমন জারীতে কাঙ্খিত মাত্রা অর্জন সম্ভবপর হয়নি। এছাড়া ভিন্ন জেলার সমন/নোটিশ জারীতে অপেক্ষাকৃত অধিকহারে প্রলম্বিত হওয়ার প্রবণতার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, নেজারতের কর্মচারী ও জারীকারকদের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ অহরহ পাওয়া যায়, যা এখন মহামারীর পর্যায়ে পৌছেছে।
সুপারিশ:
ক) সমন জারী সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিক তদারকি করা বিশেষ প্রয়োজন।
খ) জারীকারকের সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করতে হবে।
গ) জারীকারকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
ঘ) জারীকারকদের বেতন বৃদ্ধি সহ প্রতিটি জারীর জন্য পর্যাপ্ত রাহা খরচ ও incentive হিসাবে ভাতা প্রদান করতে হবে।
ঙ) দেওয়ানি কার্যবিধিতে ভিন্ন জেলায় সমন/নোটিশ জারীতে অস্বাভাবিক বিলম্ব রোধে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা জজকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনা প্রয়োজন।
(চ) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অসদাচরণ (misconduct) প্রমাণিত হলে বরখাস্ত করাসহ কঠিন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২। বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্বের প্রবণতা:
অনেক সময়ই মামলার বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিলের জন্য পুনঃপুনঃ সময় নেয়ার মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রিতায় ভূমিকা রাখে।
সুপারিশ:
সময় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারককে আইনে নির্ধারিত বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
৩। বাদীপক্ষ কর্তৃক পুনঃপুনঃ আরজি সংশোধন:
অনেক সময়েই জরুরী প্রয়োজনে বাদীপক্ষ মামলার প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি ব্যতিরেকে মামলা, দায়ের করতে বাধ্য হয়। ফলশ্রুতিতে বাদীপক্ষকে পরবর্তীতে আরজি সংশোধনের দরখাস্ত আনয়ন করতে হয়। আবার এ ধরনের দরখাস্ত পুনঃ পুনঃ দাখিল ও মঞ্জুর হলে অনেকক্ষেত্রেই নতুন করে তদ্বির গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিংবা অনেকক্ষেত্রে বিবাদীপক্ষকে অতিরিক্ত জবাব দাখিলের সুযোগ দিতে হয়। যার ফলে সামগ্রিকভাবে মামলার বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতে থাকে।
উল্লেখ্য এ সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে যখন মামলার বাদীপক্ষ বিচার স্তরে (কখনো কখনো। সাক্ষ্য গ্রহণের শেষ পর্যায়ে) এ ধরণের দরখাস্ত আনয়ন করে।
সুপারিশ:
বাদীপক্ষের আরজি সংশোধনের পৌনঃপুনিকতা ও বিবাদীপক্ষের। লিখিত জবাব দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্ব রোধকরণে আদালতসমূহ কর্তৃক আইনের বিধান দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা।
৫। বাদীপক্ষে প্রয়োজনীয় তদবির গ্রহণে সময়ক্ষেপনের প্রবণতা:
দেওয়ানী আদালতসমূহের দেওয়ানী মামলার পরিসংখ্যান নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা বাদীপক্ষের প্রয়োজনীয় তদ্বির গ্রহণে অনীহা বা অহেতুক সময়ক্ষেপনের কারণে বিলম্বিত হয়।
তাছাড়া বন্টনের মোকদ্দমায় বিবাদীপক্ষের মৃত্যুজনিত কারণে ওয়ারিশদের নাম, ঠিকানা সংগ্রহ ও তাদের কায়েম মোকামসহ প্রসেস জারী করার ব্যাপারে বাদীপক্ষ কর্তৃক অহেতুক সময় নেয়ার কারণে উক্ত মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়।
সুপারিশ:
এক্ষেত্রে সময় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারককে আইনে নির্ধারিত বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
৬। দেওয়ানী আদালতসমূহে ছানী মামলার আধিক্য:
একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের অব্যবহিত পর থেকেই উক্ত মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রিতার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনেক সময় একতরফা কিংবা আংশিক দোতরফা সূত্রে একটি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হলে অনেকক্ষেত্রেই উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ছানী মামলা দায়ের হয় এবং এতে মূল মামলা দীর্ঘসূত্রিতার নতুন মাত্রা পায়। ফলে প্রাথমিকভাবে নিষ্পত্তি হবার পরেও একটি মামলা বছরের পর বছর ছানী মামলা আকারে আদালতে বিচারাধীনথাকে এবং উক্ত ছানী মঞ্জুর হলে মূল মামলাটি নুতন করে আরম্ভ হয়। অনেকক্ষেত্রেই উপর্যুক্ত সামগ্রিক প্রক্রিয়া কোন একটি মামলাকে বছরের পর বছর প্রলম্বিত করে। আবার বিবাদীপক্ষও একজন একজন করে ছানি মামলা করে ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা দীর্ঘায়িত করে।
সুপারিশ:
ছানি মামলাসমূহ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আইনে প্রদত্ত বিধিবিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
৭। আপীল আদালত কর্তৃক পুনঃবিচারে প্রেরণের প্রবণতা:
অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আপীল আদালতসমূহের পক্ষে কোন একটি আপীন নিষ্পত্তি করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে উক্ত মামলা নিম্ন আদালতে পুনরায় বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ কারণে দেওয়ানি মামলায় দীর্ঘসূত্রিতার উদ্ভব ঘটে।
আবার কখনো দেখা যায় যে, পুনঃ বিচারে মামলা প্রেরণ করার পরে অনেকসময়ই মামলার পক্ষসমূহ সংশ্লিয় আদেশের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তদ্বির গ্রহণে অহেতুক সময়ক্ষেপন করে, যার ফলে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।
সুপারিশ
সাক্ষ্য গ্রহণসহ আশীব আদালতের বিচারিক আদালতের সকল ক্ষমতা রয়েছে বিধায় পুনঃবিচারের জন্য না পাঠিয়ে আপীল আদালতেই যথাসম্ভব মামলাটি নিষ্পত্তি করাই সঙ্গত। তাতে উভয় পক্ষেরই সময়, পরিশ্রম ও ব্যয় অনেকাংশে লাঘব হবে।
দেওয়ানি আপীল ও রিভিশন আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:
আপীল আদালতসমূহে দেওয়ানী আপীল ও রিভিশন মোকদ্দমার বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার কারণসমূহঃ
১। নথিতে এল.সি.আর. সামিল হতে দেরী হওয়া।
২। ভিন্ন জেলার নোটিশ বারবার গরজারী হওয়া বা নোটিশ জারীতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়া।
৩। আপীলকারী পক্ষের প্রয়োজনীয় তদবিরের অভাব কিংবা তদবির গ্রহণে অস্বাভাবিক বিলম্ব করা:
৪। আপীলের মেমোতে নোটিশ জারীর ঠিকানা সঠিক না থাকা:
৫। রেসপনডেন্ট এর মৃত্যুতে প্রয়োজনীয় তদবিরের অভাব।
৬। আপীলের মেমোতে পুনঃপুনঃ সংশোধন আনয়ন:
৭। বিশেষজ্ঞ মতামত সম্পর্কিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী গ্রহণে অহেতুক সময়ক্ষেপন।
৮। অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণে মামলার পক্ষসমূহের সময়ক্ষেপন।
৯। আপীলের বিভিন্ন পর্যায়ে পক্ষগণের অতিরিক্ত সময় গ্রহণ ও কালক্ষেপন।
১০। তলবকৃত নথি প্রেরণে বিলম্ব।
১১। ৮০৩ কারণে মামলা চূড়ান্ত শুনানি (PH) এর তালিকা হতে প্রত্যাহার।
সুপারিশ:
উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানে আইনে উল্লিখিত বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
তাছাড়া জেলা জজ উক্ত বিষয়সমূহে CRO অনুসারে নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।
জারী মামলার ক্ষেত্রে:
দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক রায় ও ডিক্রি ঘোষণাঅন্তে যে পক্ষের অনুকূলে রায় ঘোষিত হয় তার স্বাভাবিক প্রত্যাশা থাকে যে রায়টি দ্রুত কার্যকর হবে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত The Code of Civil Procedure, 1908 এর জারী সংক্রান্ত বিধান অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ, ফলে অন্যান্য মামলার ন্যায় জারী মামলার সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রকাশিত ১ জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশের মামলার পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় বিচারাধীন সকল প্রকার জারী মামলার মোট সংখ্যা ৯৫,৫০২ টি, যা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া একটি জারী মামলায় নানাধরণের ধাপ অনুসরণ করার বিধি বিধান থাকায় উক্ত ধাপসমূহ অনুসরণপূর্বক মামলা নিষ্পত্তি অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। অধিকন্তু, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জারী মামলায় অন্য বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতাও প্রয়োজন হয়। দেশের অধস্তন দেওয়ানি আদালতের অনিষ্পন্ন জারী মামলার প্রবণতা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে জারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৃথক কোন আদালত বা বিচারক না থাকায় একই বিচারকের পক্ষে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি, সাক্ষ্যগ্রহণ, অর্ন্তবর্তী আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি দুরূহ হয়ে পড়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে জারী মামলার কার্যক্রমের সঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবীদের সংশ্লিষ্টতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বাস্তবতা এই যে বিজ্ঞ আইনজীবীগণের জারী মামলা নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় একই বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। ফলে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়। তাহাড়া সার্ভে বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিজ্ঞ আইনজীবীর অপ্রতুলতা বাটোয়ারা মোকদ্দমা জারীর কার্যক্রমকে দীর্ঘায়িত করে। আইনের বিধান অনুযায়ী জারী কার্যক্রমে অনেক ক্ষেত্রে আদালতকে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত প্রশাসনের পক্ষ হতে প্রেরিত জনবল ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ফি-এর পরিমাণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান না থাকায় তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালতকে অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলশ্রুতিতে জারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।
লক্ষ্যণীয় যে জারী মামলার কার্যক্রম পরিচালনায় একজন বিচারক, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কী কী ভূমিকা রয়েছে বা কিভাবে উক্ত কার্যক্রম সহজসাধ্য ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা যায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা ও তদারকির অভাব জারী মামলা নিষ্পত্তিতে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।
বাস্তবতায় দেখা যায় জারী মামলাকে বিলম্বিত করার জন্য বা ফলপ্রসূ নিষ্পত্তিতে বাধা প্রদানের লক্ষ্যে অনেক দালাল শ্রেণির লোকসহ আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। বিধায় আদালতের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দ্রুততম সময়ে ও কার্যকরভাবে জারী মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হয়না। তাছাড়া, কতিপয় মামলাবাজ ব্যক্তি বা আইনজীবী জারী মামলার কার্যক্রম যাতে নিষ্পত্তি না হয় সে বিষয়ে নানা অজুহাতে দরখাস্ত দায়ের করে জারী কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করে। তাদের দৌরাত্ম্য রোধ করা আদালতের একার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় মামলার পক্ষ দ্রুততম সময়ের মধ্যে আদালতের রায়ের সুফল ভোগ করতে ব্যর্থ হয়।
অধিকন্তু, মূল মামলা নিষ্পত্তি পরবর্তী আপীল বা রিভিশন আদালতসহ উচ্চ আদালত কর্তৃক অনির্দিষ্ট কালের জন্য জারী মামলার কার্যক্রমের উপর স্থগিত আদেশ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে উিক্ত জারী মামলাটি দীর্ঘদিন যাবত অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে।
সুপারিশ:
১। বর্তমানে প্রচলিত The Code of Civil Procedure, 1908 এর জারী সংক্রান্ত বিধান অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত সংশোধন আনয়ন করা প্রয়োজন।
২। জারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে জারী মামলা আদালত (Designated Execution Court) পদ সৃজন করে একজন জ্যেষ্ঠ বিচারিক কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে জারী মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে। উক্ত আদালতের একমাত্র দায়িত্ব হবে জেলার সকল জারী মামলা পরিচালনা ও নিষ্পত্তি করা এবং এক্ষেত্রে উক্ত বিচারকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
৩। জারী মামলার কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪। জারী মামলার কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীদের সার্ভে বিষয়ে অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধকরণে বার ও বেঞ্চের সমন্বয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫। জারী কার্যক্রমে নির্বাহী ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ হতে প্রেরিত জনবল ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব পালনে ব্যয়ভার প্রদানের নিমিত্ত দূরত্ব ও জনবলের সংখ্যা বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট ফিস নির্ধারণ করতে হবে।
৬। সহজসাধ্য ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে জারী মামলার কার্যক্রম নিষ্পন্ন করার নিমিত্ত বিচারক, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ভূমিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭। জারী মামলাকে বিলম্বিত করার জন্য বা ফলপ্রসূ নিষ্পত্তিতে বাধা প্রদানের লক্ষ্যে কোনো দালাল শ্রেণির লোকসহ আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা যাতে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়ে আদালতকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। এ বিষয়ে কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
৮। জারী মামলা যাতে দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় যে লক্ষ্যে জারী মামলা কার্যক্রমের উপর স্থগিত আদেশ প্রদানকারী আদালতকে দাখিলী আপত্তি, আপীল, রিভিশন, রীট বিষয়ে দ্রুতসময়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করতে হবে।
৯। বাটোয়ারা সহ অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে চলমান জারী মামলায় কোন পক্ষের মৃত্যুজনিত কারণে জারী কার্যক্রমকে প্রলম্বিত না করে স্বল্প সময়ের মধ্যে কায়েম মোকাম করে কার্যক্রমকে চলমান রাখতে হবে। কায়েম মোকামের ক্ষেত্রে প্রকৃত ওয়ারিশদের উপর যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নোটিশ জারী হয় সে বিষয়ে আদালতকে সজাগ থাকতে হবে।
১০। বাটোয়ারাসহ অন্যান্য জারী মামলায় তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হওয়ার আবেদন করলে বস্তুতপক্ষে উক্ত পক্ষের আবেদনের কতটুকু সারবত্ত্বর আছে বা মামলার নালিশী জমিতে উক্ত তৃতীয় পক্ষের প্রকৃত স্বার্থ, স্বত্ব ও অধিকার নিহিত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে জারী কার্যক্রম পরিচালনাকারী আদালতকে সচেতন থাকতে হবে।
উপসংহার
এই রিসার্চের মাধ্যমে আমি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের দেওয়ানি আদালতে জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় বিরোধের নিষ্পত্তি হতে এত সময় লাগার কারণ কি। এবং এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সরকারের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যার মাধ্যমে মামলা জট অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি গুরুতর সমস্যা চিহ্নিত করেছি যেমন বিচারক সংকট,এজলাস সংকট, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা প্রবনতা ইত্যাদি।বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় মামলাজট দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা। আইনগত, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিভিন্ন কারণ এর জন্য দায়ী। দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে আইনের আধুনিকায়ন, ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ, বিচারকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিচারিক প্রশাসনের কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন। মামলার সময়সীমা নির্ধারণ ও তা কঠোরভাবে অনুসরণ, বিচারিক পদ্ধতির সহজীকরণ এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। বর্তমান বিচারব্যবস্থায় প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়িয়ে এবং প্রশাসনিক সংস্কার করে মামলা নিষ্পত্তির গতি বাড়ানো গেলে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সহজ হবে।
তথ্যসূত্র :
Statistical Report on Case Management, Bangladesh Supreme Court (January 1, 2023 – June 30, 2023.)
The Code of Civil Procedure 1908
M M Chowdhury, Civil Procedure in Bangladesh (Dhaka: Bangladesh Law Book Company 2012)
Hossain M, Introduction to Bangladesh Legal System (Dhaka: University Press Limited 2015)
Rahman M, The Law of Evidence in Bangladesh (Dhaka: New Age Publishers 2018)
S M Islam, Judicial System and Legal Reforms in Bangladesh, (Dhaka: The Bangladesh Bar Council 2016)
Bangladesh Legal Journal (BLJ)
Website: www.bangladeshlegaljournal.com