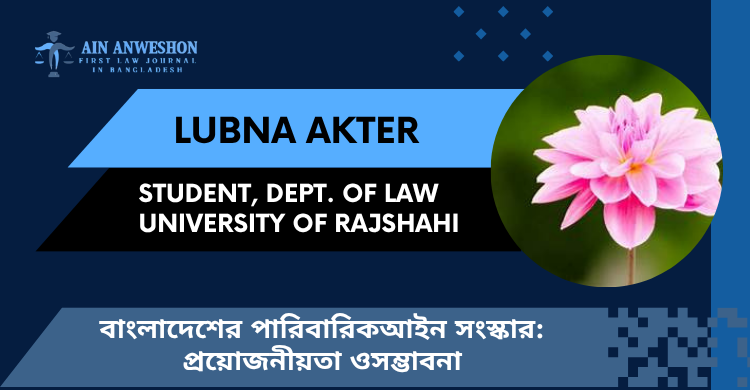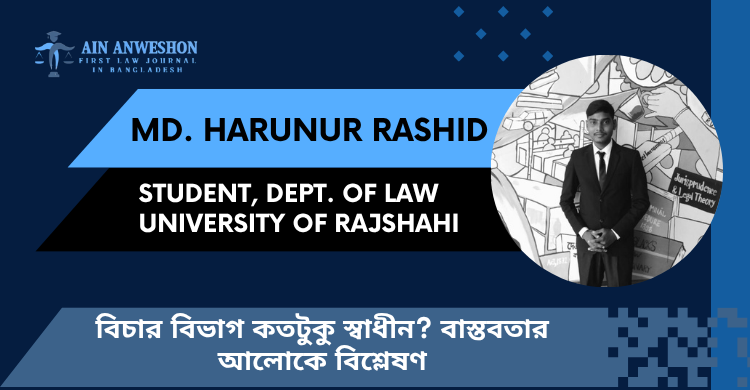ভূমিকা:
গণতন্ত্রের আদর্শ রূপে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য শাসনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাংলাদেশে এই ব্যবস্থাকে প্রায়শই একটি প্রহসন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়—যা ব্যবস্থাগত অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং সংবিধানিক আদর্শের সাথে বাস্তবতার বিচ্ছিন্নতাকে আড়াল করে। “মূর্খের শাসন” শব্দবন্ধটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি ক্রমবর্ধমান হতাশাকে প্রতিফলিত করে, যা জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ। এই নিবন্ধে বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও সংবিধানিক কাঠামোর সেইসব দিক বিশ্লেষণ করা হবে, যা এই ধারণাকে টিকিয়ে রেখেছে—কীভাবে কাঠামোগত ত্রুটি ও সামাজিক গতিশীলতা দেশের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করে দিচ্ছে।
১. সামাজিক প্রেক্ষাপট: শিক্ষা, সচেতনতা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি:
১.১ সাক্ষরতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা:
বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৭৪.৭% (বিশ্বব্যাংক, ২০২২) এ উন্নীত হলেও কার্যকর সাক্ষরতা—বিশেষ করে রাজনৈতিক সচেতনতা—এখনও নিম্ন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, যা মোট জনসংখ্যার ৬১%, প্রায়ই জটিল রাজনৈতিক আলোচনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক দলগুলি এই ফাঁককে কাজে লাগিয়ে নীতির বদলে পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। এশিয়া ফাউন্ডেশনের ২০২০ সালের একটি জরিপে দেখা গেছে, গ্রামীণ এলাকার ৬৮% ভোটার দলের ইশতেহারের চেয়ে স্থানীয় নেতাদের সমর্থনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন—যা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও সচেতন সিদ্ধান্তগ্রহণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত দেয়।
১.২ মিডিয়া ও ভুল তথ্যের প্রসার:
বাংলাদেশের মিডিয়া জগৎ প্রাণবন্ত হলেও স্ব-সেন্সরশিপ ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব তথ্যের প্রবাহকে বিকৃত করে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস-এর ২০২৩ সালের সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম, যেখানে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো আইনের অপব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একই সময়ে, সামাজিক মাধ্যম ভুল তথ্যকে বহুগুণে ছড়িয়ে দিচ্ছে, যেখানে দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি প্রচারণা চালায়। এর ফলে জনগণের আস্থা ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে এবং নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হচ্ছে।
১.৩ দুর্নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা:
দুর্নীতি বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপ্ত—যা নিয়মতান্ত্রিক জটিলতা থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রচারণায়ও বিদ্যমান। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০২২ সালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৭তম। রাজনৈতিক অভিজাতরা প্রায়ই ব্যক্তিগত লাভকে জনকল্যাণের ওপর প্রাধান্য দেন। পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি এখানে প্রবল, যেখানে ভোটের বিনিময়ে সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করা হয়—এটি দীর্ঘমেয়াদি সুশাসনের পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদি লাভের সংস্কৃতি তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনের আগে ভর্তুকিযুক্ত পণ্য বিতরণ দেখায় কীভাবে রাজনৈতিক দলগুলি দৃষ্টিভঙ্গিহীন প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসমর্থন কুড়ায়।
২. সংবিধানিক কাঠামো: কাঠামোগত ত্রুটি ও প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয়:
২.১ অস্পষ্ট সংশোধনী ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ:
বাংলাদেশের সংবিধানিক ইতিহাস রাজনৈতিক সংশোধনীর দাগে ভরা। ১৫তম সংশোধনীর (২০১১) মাধ্যমে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়—যার পরবর্তী নির্বাচনগুলি (২০১৪, ২০১৮) বিরোধী দলগুলির বয়কট ও অনিয়মের অভিযোগের মুখে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে—যা ক্ষমতার ভারসাম্যকে নষ্ট করে নির্বাহী বিভাগের অত্যধিক প্রভাবকে বৈধতা দেয়।
২.২ নির্বাচনী সততার প্রশ্ন
নির্বাচনী আইন গণতান্ত্রিক মনে হলেও সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ। নির্বাচন কমিশনকে দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট হিসেবে দেখা হয়, যাদের তত্ত্বাবধানে ভোটার ভীতি ও ব্যালট বাক্সে জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে। ২০১৮ সালে ইইউ পর্যবেক্ষক মিশন “উল্লেখযোগ্য অনিয়ম” এর কথা উল্লেখ করে, যেখানে ১৭% ভোটকেন্দ্রে অবিশ্বাস্য উচ্চ ভোটার উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়। এমন ত্রুটিগুলো নির্বাচনের ফলাফলকে অবৈধ করে তোলে এবং জনগণের উদাসীনতা বাড়ায়।
২.৩ বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ
সংবিধানিক নিশ্চয়তা সত্ত্বেও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। নির্বাহী বিভাগের প্রভাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া পক্ষপাতের অভিযোগের সম্মুখীন। বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার বিতর্কিত মামলার মতো উচ্চপ্রোফাইল মামলাগুলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে দেখা হয়—যা আইনের শাসনে আস্থা হ্রাস করে।
৩. রাজনৈতিক গতিশীলতা: বংশানুক্রমিক শাসন ও মতপ্রকাশের দমন
৩.১ বংশানুক্রমিক দ্বৈত শাসন
বাংলাদেশের রাজনীতি দুটি রাজবংশ দ্বারা প্রভাবিত: আওয়ামী লীগ (শেখ হাসিনার নেতৃত্বে) ও বিএনপি (জিয়া পরিবারের নেতৃত্বে)। এই দ্বৈত শাসন নতুন চিন্তাকে স্তব্ধ করে দেয়, যেখানে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য নীতির চেয়ে প্রাধান্য পায়। তরুণ নেতারা প্রান্তিক হয়ে পড়েন—যা একটি স্থবির রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে।
৩.২ বিরোধী কণ্ঠের দমন
বিরোধী দলগুলি ব্যবস্থাগত নিপীড়নের শিকার। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপির অনুপস্থিতি—যা গণগ্রেপ্তার ও সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে—এটির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো আইনসমূহ সমালোচকদের আটকের জন্য ব্যবহার করা হয়, নিরাপত্তা বাহিনীর আধা-বিচারিক কার্যক্রম ভীতি সৃষ্টি করে। সুশীল সমাজও একই চাপের মুখে—এনজিওগুলিকে কঠোর তহবিল আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
৪. তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত: দক্ষিণ এশিয়া থেকে শিক্ষা:
ভারতের শক্তিশালী নির্বাচনী ব্যবস্থা বা শ্রীলঙ্কার বহুদলীয় প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার তুলনায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতায় পিছিয়ে। পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর প্রভাব থাকলেও বাংলাদেশে নাগরিক কর্তৃত্ববাদী শাসন বিদ্যমান—তবে উভয় দেশই গণতান্ত্রিক সুসংহতকরণে সংগ্রাম করছে। আঞ্চলিক তুলনা থেকে স্পষ্ট, বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলি অনন্য নয়—এবং অসম্ভবও নয়।
৫. সংস্কারের পথ:
১. শিক্ষার ক্ষমতায়ন: শিক্ষাক্রমে নাগরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা।
২. প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল ও নির্বাচন কমিশনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা।
৩. দুর্নীতি প্রতিরোধ: দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করে বাস্তবায়নযোগ্য নির্দেশিকা দেওয়া।
৪. মিডিয়ার স্বাধীনতা: দমনমূলক আইন বাতিল ও সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
উপসংহার:
বাংলাদেশের গণতন্ত্র একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সংবিধানিক কাঠামো থাকলেও সামাজিক বৈষম্য ও প্রতিষ্ঠানিক ক্ষয়ের কারণে “মূর্খের শাসন”-এর ধারণা শক্তিশালী হচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য কেবল আইনি সংস্কার নয়, প্রয়োজন জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতির বিকাশ। তখনই বাংলাদেশ তার গণতান্ত্রিক প্রহসনকে একটি জীবন্ত ও ন্যায়ভিত্তিক বাস্তবতায় রূপান্তর করতে পারবে।