ভূমিকা
বাংলাদেশের বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ (SPA) দেশের আইন ইতিহাসে অন্যতম বিতর্কিত আইন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে প্রণীত এই আইনটি মূলত জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে, এই আইনটি অস্পষ্ট ও বিতর্কিত ধারাসমূহ, বিচারবহির্ভূত আটকাদেশ এবং বিচারিক তদারকির অভাবের কারণে দমনমূলক এক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।
বিগত কয়েক দশক ধরে এই আইনটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমন, গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ এবং সাধারণ নাগরিকদের অন্যায়ভাবে আটক করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই এখন সময় এসেছে এই আইনটির গভীর পর্যালোচনা, সংস্কার অথবা সম্পূর্ণরূপে বাতিলের।
—
প্রধান ধারা ও বিতর্ক
১. বিচারবহির্ভূত আটকাদেশ
এই আইনের অধীনে সরকার কোনো অভিযোগ বা প্রমাণ ছাড়াই ছয় মাস পর্যন্ত কাউকে আটক রাখতে পারে, যা পরবর্তীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো সম্ভব।
এটি সরাসরি সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ (জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার) ও ৩৩ অনুচ্ছেদ (বিচারবহির্ভূত আটকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা) লঙ্ঘন করে।
বিচার বিভাগীয় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই, ফলে নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকে।
২. অর্থনৈতিক অপরাধের জন্য চরম শাস্তি
চোরাচালান, মজুতদারি ও নাশকতা সংক্রান্ত অপরাধের জন্য এই আইনে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।
এতে শাস্তির মাত্রা অতিরিক্ত কঠোর ও অপ্রাসঙ্গিক, যা রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে।
৩. বিচারিক তদারকির অভাব
আদালত এই আইনের অধীনে হওয়া আটকাদেশের উপর খুবই সীমিত হস্তক্ষেপ করতে পারে।
অনেক বন্দি বছরের পর বছর বিচার ছাড়াই আটক থাকে, যা ন্যায়বিচারের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।
৪. রাজনৈতিক দমন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন
বিভিন্ন সরকার এই আইন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের দমন করতে ব্যবহার করেছে।
অন্যায় আটক, জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি, হেফাজতে নির্যাতন এবং দীর্ঘমেয়াদী বন্দিত্বের বহু অভিযোগ রয়েছে।
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন করায় এই আইন সরাসরি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।
—
জরুরি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা
বাংলাদেশের বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের জন্য এক গুরুতর হুমকি। এই আইন সংস্কার না করা হলে এটি সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকারের প্রতি চরম অবমাননা হিসেবে থেকে যাবে। নিচে এই আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:
১. আইনটি সম্পূর্ণ বাতিল বা বড় ধরনের সংশোধন
সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হলো এই আইনটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে সংবিধানসম্মত ও মানবাধিকার-বান্ধব নতুন আইন প্রণয়ন করা।
যদি তাৎক্ষণিক বাতিল করা সম্ভব না হয়, তবে নিম্নলিখিত সংশোধনগুলো জরুরি:
আটকাদেশের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে, যাতে অযৌক্তিকভাবে আটক রাখার সুযোগ না থাকে।
অপরাধের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে হবে, যাতে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থে এর অপব্যবহার না হয়।
অর্থনৈতিক অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বাতিল করতে হবে এবং এর পরিবর্তে যৌক্তিক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
২. বিচার বিভাগীয় তদারকি ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা
আদালতের সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত এই আইনের অধীনে হওয়া আটকাদেশ পর্যালোচনা করার।
আটক ব্যক্তিকে সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো ও আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে।
দ্রুত বিচারিক পর্যালোচনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা উচিত, যাতে বিচারহীন বন্দিত্ব বন্ধ হয়।
৩. রাজনৈতিক অপব্যবহার রোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
এই আইন যেন কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সাংবাদিক বা ভিন্নমতাবলম্বীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
যারা অন্যায়ভাবে এই আইন প্রয়োগ করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখতে হবে।
মানবাধিকার কর্মী, আইন বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের নিয়ে একটি স্বাধীন পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা দরকার, যা এই আইনের অধীনে হওয়া মামলাগুলো পর্যবেক্ষণ করবে।
৪. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুসারে সংশোধন
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি (ICCPR)-এর স্বাক্ষরকারী দেশ, যা বিচারবহির্ভূত আটক নিষিদ্ধ করে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। SPA-কে এই চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
বিকল্প নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা উচিত, যা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ রক্ষা করবে, তবে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব করবে না।
একটি সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে, যেখানে যথাযথ বিচারিক তদারকি থাকবে।
বর্তমান ফৌজদারি আইন আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে, যাতে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের আটকের জন্য SPA-এর প্রয়োজন না হয়।
৫. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্কার
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে তারা সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে, না যে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে মানুষকে আটক করতে পারে।
একটি স্বাধীন তদারকি সংস্থা গঠন করতে হবে, যা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।
উপসংহার
বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পরিপন্থী। জাতীয় নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা কখনোই সাংবিধানিক অধিকার ও ন্যায়বিচার লঙ্ঘনের কারণ হতে পারে না।
বাংলাদেশকে অবশ্যই এই আইন বাতিল অথবা বড় ধরনের সংশোধন করতে হবে। আইনের শাসন, স্বচ্ছ বিচার ও মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে, এই আইনকে আর বহাল রাখা যাবে না।
এখন প্রশ্ন হলো—বাংলাদেশ কি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পথে এগিয়ে যাবে, নাকি রাজনৈতিক দমনমূলক এই আইনটিকে বহাল রেখে জনগণের অধিকার হরণ করবে? আইনপ্রণেতাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই।




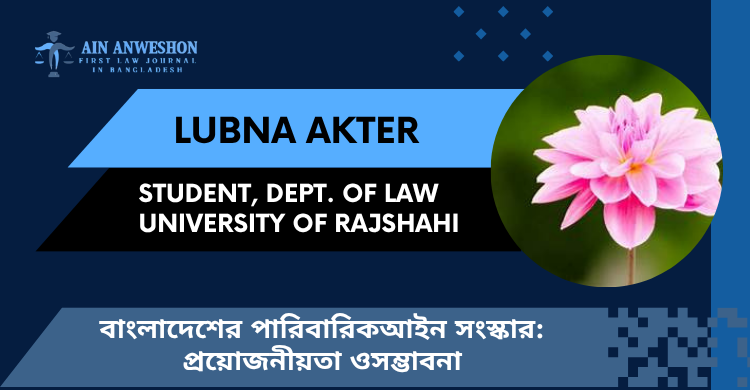




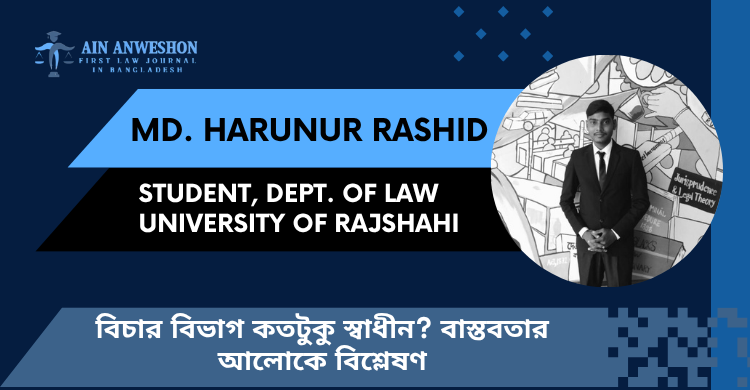







One Response
I am proud of you bondu …