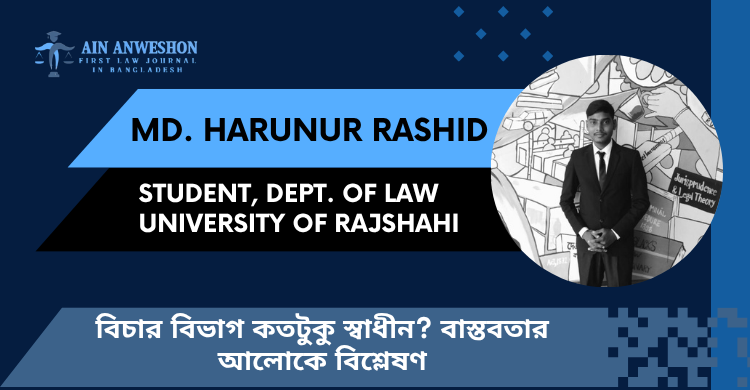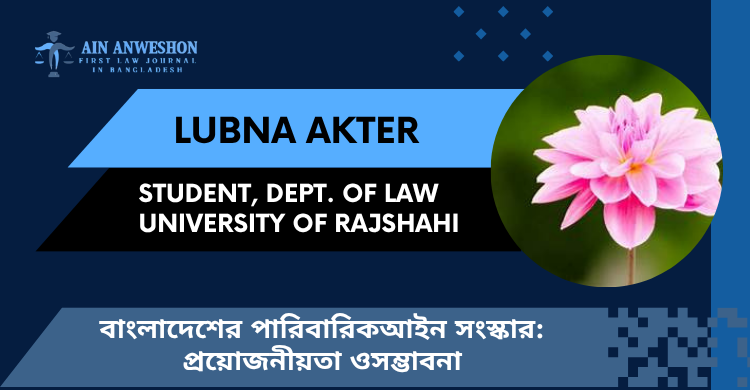বাংলাদেশের বিচার বিভাগ একটি স্বাধীন ও সমান্তরাল শাখা হিসেবে গণ্য হলেও এর প্রকৃত স্বাধীনতা এবং কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংবিধানিক এবং সামাজিক প্রভাব বিদ্যমান। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একটি সুসংগঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তবে বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেকটা সংকুচিত এবং বিতর্কিত, যা বিশেষত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং প্রশাসনিক চাপে প্রকাশ পায়।
বিচার বিভাগের সাংবিধানিক অবস্থান:
বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করতে একটি রিট করেছিলেন সাবেক জেলা জজ মাসদার হোসেন। লক্ষ্য ছিল নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা হওয়ার মাধ্যমে বিচার বিভাগ যেন রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাবমুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ১৯৯৪ সালে রিটটি দায়ের করেন তিনি। পরবর্তীকালে চূড়ান্ত শুনানি করে ১৯৯৯ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা হয়। চূড়ান্ত সেই রায় বাস্তবায়নে ১২ দফা নির্দেশনা দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এর ফলে ২০০৭ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা হয়।
বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগকে একটি স্বাধীন অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ‘রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন৷’ উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি স্বাধীন বিচার বিভাগের রক্ষাকবচ। হস্তক্ষেপমুক্ত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচার বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই স্বাধীনতা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা সবসময় রক্ষা করা যায় না।
১৯৭২ সালের সংবিধানে বলা হয়, জেলা জজদের নিয়োগ দেওয়া হবে সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশক্রমে এবং নিম্ন আদালতের সব বিচারকের কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরির ক্ষমতা শুধু উচ্চ আদালতের হাতে থাকবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য প্রণীত এসব বিধান সংবিধানে অবিকৃত থাকেনি। চতুর্থ সংশোধনী জারি করে তিন বছরের মাথায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।
এরপর নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ এখন মূলত সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। মাসদার হোসেন মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকদের নিয়োগের জন্য আলাদা কমিশন, তাঁদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির নানান বিধান হয়েছে, কিন্তু সরকারের খবরদারি রোধে সেগুলো তেমন একটা ভূমিকা রাখেনি।
বাংলাদেশে নিম্ন আদালতের বিচারকেরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন বলে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগের সুযোগ নেই। তবে সেখানে পরীক্ষার সকল ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও পুলিশ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে কারও নিয়োগ আটকে দেওয়া সম্ভব, এসব ঘটনা ঘটছেও দেশে।
বাংলাদেশে নিম্ন আদালতের বিচারকদের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ শুরু হয় মূলত নিয়োগপ্রক্রিয়ার পর। এর প্রতিটি স্তরে (পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, শৃঙ্খলা) নিম্ন আদালতের বিচারকেরা থাকেন আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এখানে উচ্চ আদালতের সঙ্গে পরামর্শের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু সিনিয়রদের ডিঙিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক বিবেচনায় বদলির ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে উচ্চ আদালত দ্বিমত করে না।
বিচার বিভাগের কোন নিয়ন্ত্রণ যদি নির্বাহী বিভাগে থাকে অর্থাৎ সোজা কথায় আইন মন্ত্রণালয় যদি বিচারকদের নিয়োগ-পদোন্নতি ইত্যাদির ওপর কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হয়নি। আমাদের অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ যৌথভাবে আইন মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রিম কোর্টে আছে। সুতরাং বলা যায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিচার বিভাগ স্বাধীন না।
নিম্ন আদালতের তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে সরকারের নিয়ন্ত্রণের সুযোগ রয়েছে আরও বেশি। হাইকোর্টে বিচারক পদে নিয়োগ হয় সম্পূর্ণভাবে সরকারের মর্জিমতো। রাজনৈতিক মামলায় বিচারকেরা প্রতিকার দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁদেরকে নানা হুমকির সম্মুখীন হতে হয়।
অযাচিত রাজনৈতিক প্রভাব ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:
বাংলাদেশের বিচার বিভাগ অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাবের শিকার হয়েছে। রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত বিচারিক কার্যক্রম যেমন– উচ্চ আদালতের আদেশ, সরকারের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি বা বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান, এসব ক্ষেত্রে অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দেখা যায়। অনেক সময় সরকারের পক্ষ থেকে বিচারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, যা তাঁদের স্বাধীনতার উপর প্রশ্ন তোলে।
এছাড়া ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিরা কখনও কখনও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করতে পারেন, এমনকি বিচারকদের নিয়োগ এবং বদলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারেন। এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সংকীর্ণ করে এবং জনগণের বিশ্বাসকে আঘাত করে। বাংলাদেশে বহু মামলা দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলে থাকে, যা বিচার বিভাগের কার্যক্ষমতা এবং স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতি:
বাংলাদেশে বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং পদত্যাগের প্রক্রিয়া সাংবিধানিকভাবে স্বতন্ত্র হলেও বাস্তবে এটি রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে থাকে। সংসদের মাধ্যমেই বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় যেখানে সরকার তথা ক্ষমতাসীন দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলস্বরূপ, বিচার বিভাগের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক স্বার্থ ও পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা তৈরি হয়।
বাংলাদেশের বিচার বিভাগে স্বাধীনতার ধারণা সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বাস্তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নানা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা শুধু সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য বিচার বিভাগের প্রতি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানো, বিচারকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করা এবং বিচারিক অবকাঠামো শক্তিশালী করা অতীব জরুরি।