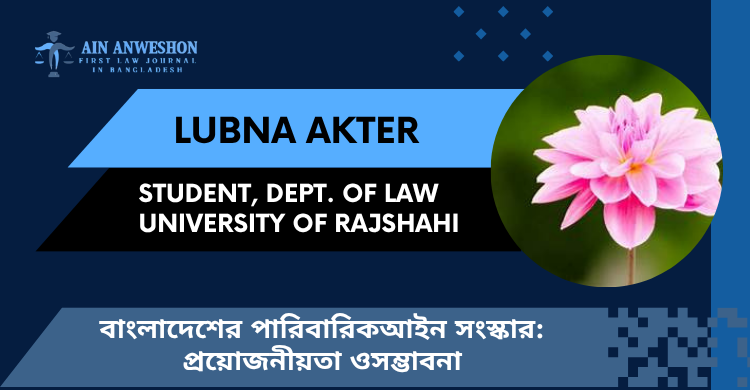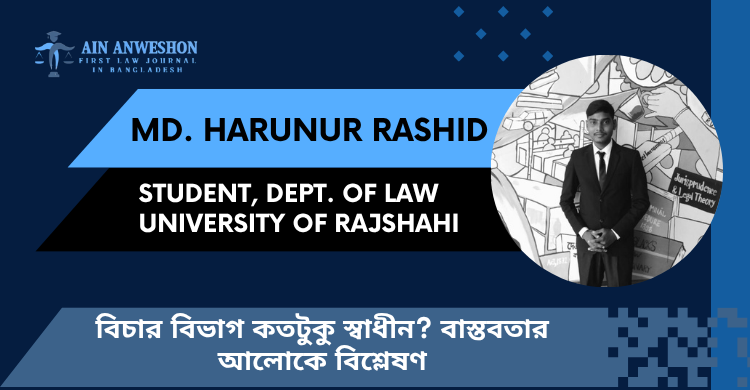শৈশব থেকেই আমি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের বিলম্বের গল্প বহুবার শুনেছি, যেখানে একটি মামলা বছরের পর বছর চলতে থাকে। এই কৌতূহল আমাকে আইন নিয়ে পড়াশোনা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। একদিন, আমি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু কার্যকরী ভূমিকা রাখব। যখন আমার নামের আগে “বিচারপতি ইসরাত জাহান ইমা” লেখা হবে, তখন আমি যেন প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারি। এখন, আমি ফেডারেল বা বিকেন্দ্রীভূত সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং “বিকেন্দ্রীভূত সরকার কতটুকু কার্যকর হতে পারে?” সে বিষয়েও আলোচনা করব।
প্রথমে একটি প্রশ্ন আসে – “ফেডারেল বা বিকেন্দ্রীভূত সরকার কী?”
ফেডারেল সরকার এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় (জাতীয়) সরকার ও আঞ্চলিক (রাজ্য, প্রাদেশিক বা স্থানীয়) সরকারের মধ্যে বিভক্ত থাকে। অন্যদিকে, বিকেন্দ্রীভূত সরকার এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার তার কিছু ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারকে অর্পণ করে।
ফেডারেল এবং বিকেন্দ্রীভূত সরকারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো:
ফেডারেল সরকারব্যবস্থায়, সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ভাগ করা হয়।
বিকেন্দ্রীভূত সরকারব্যবস্থায়, কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা অর্পণ করে, তবে প্রয়োজনে তা ফিরিয়ে নিতে পারে, কারণ এটি সাংবিধানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়।
বাংলাদেশে ফেডারেল সরকারব্যবস্থা চালুর যৌক্তিকতা
যে কারণে এটি যৌক্তিক:
১. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং এটি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় প্রশাসনের উপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, যা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। একটি ফেডারেল ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারকে তাদের অঞ্চলের উন্নয়ন ও নীতিনির্ধারণে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিতে পারে।
২.সমন্বিত আঞ্চলিক উন্নয়ন: বাংলাদেশের উন্নয়ন মূলত ঢাকা এবং কয়েকটি প্রধান শহরকেন্দ্রিক। একটি ফেডারেল ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজ্য বা প্রদেশ তাদের নিজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করতে পারবে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।
৩.জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি: চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা, সিলেট এবং অন্যান্য অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। যদি এই অঞ্চলগুলো আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন পায়, তবে তারা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় বজায় রাখতে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।
৪.রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা: কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশে অস্থিরতার কারণ হতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন থাকলে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংকটের প্রভাব কিছুটা কমে আসবে।
যে কারণে এটি অযৌক্তিক:
১.জাতীয় সংহতির ঝুঁকি: বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ এবং এখানে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্য বিদ্যমান। একটি অনিয়ন্ত্রিত বিকেন্দ্রীকরণ বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে, যা জাতীয় স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হতে পারে।
২. বিচ্ছিন্নতাবাদের সম্ভাবনা: নির্দিষ্ট অঞ্চলে বেশি স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলে তারা ভবিষ্যতে স্বাধীনতার দাবি তুলতে পারে, যা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষত সংবেদনশীল অঞ্চল যেমন চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।
৩. প্রশাসনিক জটিলতা ও ব্যয় বৃদ্ধি: নতুন প্রদেশ বা রাজ্য তৈরি করতে হলে আলাদা প্রশাসন, আইনসভা এবং অন্যান্য সরকারি কাঠামো গঠন করতে হবে, যা সরকারি ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।
৪.দুর্নীতি ও অদক্ষ শাসন ব্যবস্থার ঝুঁকি: যদি আঞ্চলিক সরকারগুলো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মতো সেগুলোও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারে, যা শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা নষ্ট করবে।
বাংলাদেশের জন্য সমাধান কী?
বর্তমান বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশে সরাসরি ফেডারেল ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা খুব একটা যৌক্তিক মনে হয় না। প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে চারটি প্রদেশে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর) বিভক্ত করা হবে এবং সংসদ সদস্যের সংখ্যা হবে ৫০৫। এখানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত উন্নত, যা রংপুর ও রাজশাহীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে, যেমন:
1. স্থানীয় সরকারকে আরও বেশি ক্ষমতায়ন করা।
2.জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনকে অধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া।
3.উন্নয়ন বাজেটের সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করা।
4.ঢাকার পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগেও গার্মেন্টস ও কলকারখানা স্থানান্তর করা।
কেন স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি?
বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ অঞ্চলভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, গণতন্ত্রের প্রসার এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা অনেক সময় স্থানীয় সমস্যার যথাযথ সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু বিকেন্দ্রীভূত সরকারব্যবস্থায় স্থানীয় প্রশাসন স্বতন্ত্র প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে, যা আরও কার্যকর সমাধান আনতে পারে।
এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ৬৫% লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম প্রয়োজন। অর্থাৎ, বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে।
বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের প্রভাব
বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার বাড়বে, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে। এটি যাতায়াত ব্যয় ও সময় কমিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য আইনি সহায়তা সহজ করবে।
সুবিধাসমূহ:
i.মামলার জট কমবে, নিম্ন আদালত ছোটখাট মামলা নিষ্পত্তি করতে পারবে, ফলে উচ্চ আদালত বড় ও জটিল মামলাগুলোতে মনোযোগ দিতে পারবে।
ii.বিচারব্যবস্থা আরও দক্ষ ও গণমুখী হবে।
iii.বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা বাড়বে এবং স্থানীয় সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।
চ্যালেঞ্জসমূহ:
i.বিভিন্ন অঞ্চলে আইন ভিন্নভাবে প্রয়োগ হতে পারে, যা স্ববিরোধী আইনি ব্যাখ্যার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
ii.স্থানীয় রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে পারে, যা ন্যায়বিচারের পথে বাধা হতে পারে।
iii.পর্যাপ্ত তদারকি ও সম্পদের অভাব থাকলে দুর্নীতি ও অনিয়মের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।
বাংলাদেশে সরাসরি ফেডারেল ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে। তবে, প্রশাসনিক ও বিচারিক বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্যই প্রয়োজন। এটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে পূরণ হবে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।