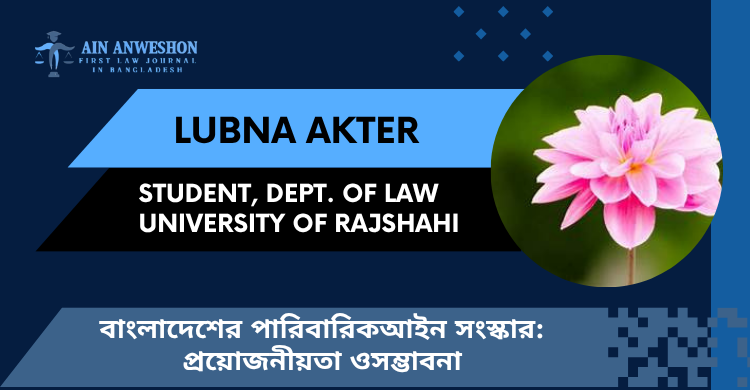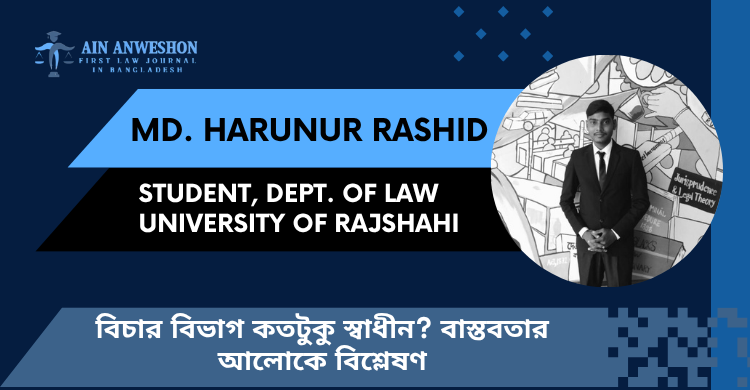দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ বা আইনসভা হলো এমন একটি আইনসভা যা দুটি পৃথক কক্ষ নিয়ে গঠিত। যেখানে একটি কক্ষকে “উচ্চকক্ষ”; অন্যটিকে “নিম্নকক্ষ” বলা হয়। এই ধরনের আইনসভায় আইন প্রণয়নে সমান ক্ষমতার ভারসাম্য বা “চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স” নিশ্চিত করা হয়।
এই ধরনের আইনসভায় নিম্নকক্ষের সদস্যরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। তাদের হাতেই থাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। তবে আইন কার্যকর করতে উচ্চকক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় জনগণের প্রতিনিধি তথা নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছামতো আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারেন না।
আর উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের উচ্চকক্ষের সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হন; যুক্তরাজ্যে “হাউস অব লর্ডস” নীতির মাধ্যমে উচ্চকক্ষের সদস্য নিযুক্ত করা হয়; প্রতিবেশি দেশ ভারতে সংসদের সদস্যদের দ্বারা উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হয়।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দায়িত্ব নেয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ছাত্র-জনতার দাবির মুখে রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেয় সরকার। এজন্য ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়।
রাষ্ট্র সংস্কারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে ইতোমধ্যে প্রতিবেদন দিয়েছে ৪টি সংস্কার কমিশন।
এগুলোর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তবনায় সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া কমিশন দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ চালু করার জন্য সুপারিশ করেছে।
দ্বিকক্ষ সংসদের বিষয়ে যা রয়েছে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনায়:
বাংলাদেশের বর্তমান এক কক্ষের জাতীয় সংসদে মোট আসন ৩৫০টি। যার মধ্যে ৩০০টি আসনে সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। আর ৫০টি আসন থাকে নারীদের জন্য সংরক্ষিত। সাধারণ নির্বাচনে পাওয়া আসনের অনুপাতে এসব আসন বণ্টন করা হয়।
তবে সংবিধান সংস্কার কমিশনের খসড়া প্রস্তাবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের বিষয়ে বলা হয়েছে, নিম্নকক্ষ থাকবে ৪০০টি আসন। আর উচ্চকক্ষে থাকবে ১০৫টি আসন।
নিম্নকক্ষের ৪০০টি আসনে প্রচলিত ব্যবস্থায় অর্থাৎ সরাসরি জনগেণর ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন।
উচ্চকক্ষের ১০০টি আসনে নির্বাচন হবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে সারাদেশে মোট যত ভোট পাবে; সেই অনুপাতে তারা উচ্চকক্ষে আসন পাবে। তবে উচ্চকক্ষে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের কথাও বলা হয়েছে সংবিধান সংস্কার কমিটির সুপারিশে।
উচ্চকক্ষের বাকি ৫টি আসন থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে। সমাজের পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে এই পাঁচ আসনে সংসদ সদস্য মনোনয়ন দেবেন রাষ্ট্রপতি।
দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ
১. সংবিধান সংশোধনের বাধা
বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে (Article 65) এককক্ষবিশিষ্ট সংসদের কথা বলা হয়েছে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু করতে হলে সংবিধানের একাধিক অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যা একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।
২. এককেন্দ্রিক শাসন বনাম যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো
বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State), যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। অধিকাংশ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে দ্বিতীয় কক্ষ সাধারণত আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্বের জন্য থাকে (যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট বা ভারতের রাজ্যসভা)। কিন্তু বাংলাদেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থা না থাকায় দ্বিতীয় কক্ষের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
৩. রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রিকতা ও প্রশাসনিক জটিলতা
দ্বিতীয় কক্ষে যদি সদস্যদের মনোনীত বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত করা হয়, তবে এটি রাজনৈতিক অভিজাতদের আধিপত্য সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলীয় প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতার সমস্যা থাকায় এটি আরও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।
৪. অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যয়
একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ পরিচালনা করতে আরও বেশি বাজেট, লোকবল এবং অবকাঠামোর প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি একটি বড় আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের সম্ভাবনা
যদিও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু করা হলে বাংলাদেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা আসতে পারে।
১. আইন প্রণয়নে গুণগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি
একটি দ্বিতীয় কক্ষ থাকলে আইন প্রণয়ন আরও পর্যালোচনার সুযোগ পাবে এবং একক দলীয় আধিপত্য কমে আসবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল সংসদে প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে আইন পাসের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আলোচনা হয় না।
২. আঞ্চলিক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি
যেহেতু বাংলাদেশে উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত, তাই একটি দ্বিতীয় কক্ষ তাদের মতামত সংসদে পৌঁছানোর সুযোগ দিতে পারে। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে।
৩. রাজনৈতিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা
একটি দ্বিতীয় কক্ষ সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং নির্বাহী বিভাগের অতিরিক্ত আধিপত্য রোধ করতে পারে। এটি বাংলাদেশে অধিকতর গণতান্ত্রিক চর্চা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে সহায়ক হতে পারে।
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ ও বাস্তবায়নযোগ্যতা:
বিশ্বের অনেক এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সফলভাবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থা চালু করেছে। যেমন, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলেও তারা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করে। বাংলাদেশ চাইলে এমন একটি মডেল অনুসরণ করতে পারে, যেখানে দ্বিতীয় কক্ষটি আঞ্চলিক প্রদেশের পরিবর্তে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে।
তবে, এটি বাস্তবায়নের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করতে হবে:
সুস্পষ্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া: যাতে রাজনৈতিক অভিজাতরা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে।
আইন প্রণয়নে দ্বন্দ্ব এড়ানো: প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করা জরুরি।
সুশাসন নিশ্চিতকরণ: দ্বিতীয় কক্ষ যেন প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি না করে, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।
উপসংহার :
বাংলাদেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিতর্ক। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে এককক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থাই কার্যকর বলে মনে করা হয়, তবে দ্বিতীয় কক্ষ সংযোজন করলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হতে পারে। তবে, এটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সংলাপ, গবেষণা ও কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন।
তথ্যসূত্র :
Ahmed, Nizam. The Parliament of Bangladesh: Accountability and Performance of MPs. Routledge, 2018.
Halim, Md Abdul. Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective. CCB Foundation, 2012.
Rahman, Mizanur. “Bicameralism in Bangladesh: A Theoretical and Comparative Analysis.” Asian Journal of Comparative Politics 5, no. 2 (2020): 112–130.
Siddiqui, Kamal. Local Government in Bangladesh: Contemporary Issues and Challenges. Univity Press Limited, 2005.