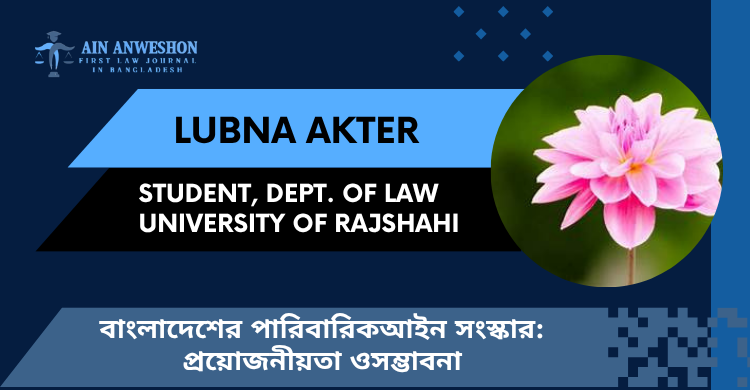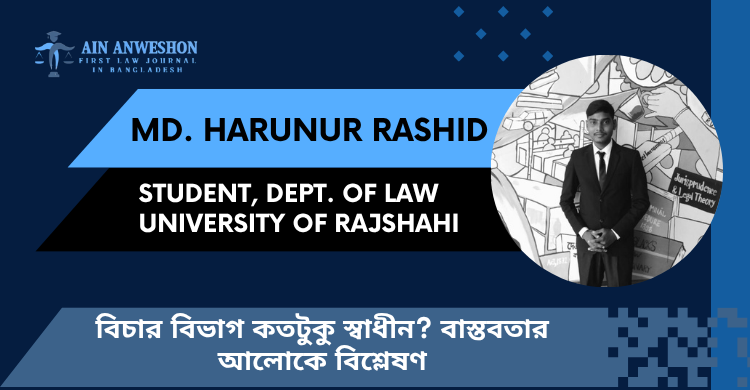ভূমিকা
বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হয়, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই প্রবন্ধে ফেডারেলিজম ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার তুলনা করা হবে এবং বাংলাদেশের সাংবিধানিক ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া শিক্ষা আলোচনা করা হবে।
ফেডারেলিজম ও ইউনিটারি রাষ্ট্র: সংজ্ঞা ও মূল ধারণা
ফেডারেলিজম: কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানি ফেডারেল মডেল অনুসরণ করে।
ইউনিটারি রাষ্ট্র: সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং স্থানীয় প্রশাসনগুলি এর অধীনেই পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জাপান এই পদ্ধতি অনুসরণ করে।
ফেডারেল ব্যবস্থার সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ
সুবিধা:
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন: স্থানীয় সরকার নিজস্ব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়।
জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ: শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নাগরিকদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে।
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সুরক্ষা: বহুজাতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর জন্য এটি কার্যকর, যেমনটি ভারত ও সুইজারল্যান্ডে দেখা যায়।
ক্ষমতার ভারসাম্য: কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের ফলে একনায়কতন্ত্রের সম্ভাবনা কমে।
উন্নয়নের ভারসাম্য: প্রতিটি অঞ্চল নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।
চ্যালেঞ্জ:
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ঝুঁকি: অত্যধিক স্বায়ত্তশাসন বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা তৈরি করতে পারে, যেমন স্পেনের কাতালোনিয়ায় দেখা যায়।
প্রশাসনিক জটিলতা: একাধিক স্তরের সরকার থাকার ফলে নীতি প্রয়োগে জটিলতা দেখা দিতে পারে।
অর্থনৈতিক বৈষম্য: কিছু অঞ্চল বেশি উন্নত হতে পারে, যা অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে।
সংঘাত ও মতপার্থক্য: আঞ্চলিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে।
ইউনিটারি রাষ্ট্রব্যবস্থার সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ
সুবিধা:
শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন: দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর শাসন সম্ভব হয়।
জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণ: প্রশাসনিক বিভাজন কম থাকায় জাতীয় সংহতি বজায় থাকে।
প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস: কেন্দ্রীভূত প্রশাসন পরিচালনার খরচ কম হয়।
আইন ও নীতির সামঞ্জস্য: সমগ্র দেশে অভিন্ন আইন ও নীতি কার্যকর থাকায় শাসনব্যবস্থা স্থিতিশীল হয়।
দ্রুত নীতিনির্ধারণ: সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় ও প্রশাসনিক জটিলতা কম থাকে।
চ্যালেঞ্জ:
স্থানীয় চাহিদা উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা: কেন্দ্রীয় সরকার সবসময় স্থানীয় সমস্যার যথাযথ সমাধান দিতে পারে না।
ক্ষমতার অপব্যবহার: কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা একনায়কতান্ত্রিক শাসনের দিকে ধাবিত করতে পারে।
নীতির সীমিত উদ্ভাবন: কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত নীতিগুলো সব অঞ্চলের জন্য কার্যকর নাও হতে পারে।
উন্নয়নের অসমতা: কিছু অঞ্চল উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা
ভারত:
ভারত একটি ফেডারেল রাষ্ট্র যেখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন রয়েছে।
তবে সংবিধানে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা বজায় রাখা হয়েছে।
যুক্তরাজ্য:
যুক্তরাজ্য একটি ইউনিটারি রাষ্ট্র হলেও স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডকে কিছু স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছে।
ইথিওপিয়া:
ইথিওপিয়ার সংবিধান জাতিগোষ্ঠীগুলোকে স্বায়ত্তশাসন এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দেয়, যা দেশের স্থিতিশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
বাংলাদেশের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ: কোন পথ বেছে নেওয়া উচিত?
স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ: উপজেলা ও জেলা পরিষদের ক্ষমতা বাড়িয়ে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিকেন্দ্রীকরণ: পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো সংবেদনশীল এলাকায় আরও কার্যকর স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা।
প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ: কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব আঞ্চলিক পর্যায়ে হস্তান্তর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি বৃদ্ধি করা।
স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা: প্রতিটি অঞ্চলের উন্নয়ন চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
উপসংহার
বাংলাদেশের জন্য সরাসরি ফেডারেল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি শক্তিশালী ইউনিটারি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই কিছু বিকেন্দ্রীকরণমূলক নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারগুলো আরও কার্যকর হবে, কিন্তু জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকবে।