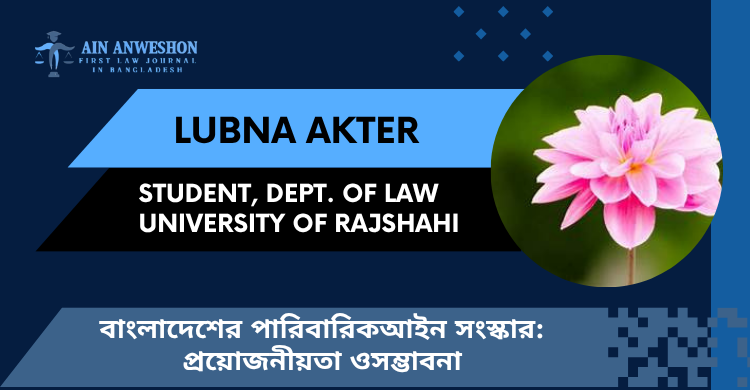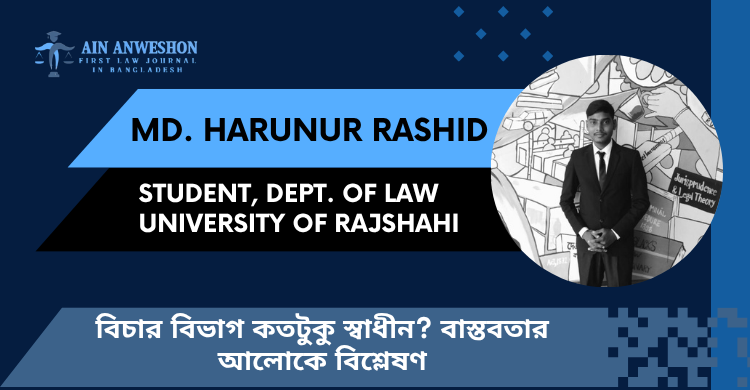৫ জানুয়ারি, ২০২৫। পত্রিকার পাতা খুলতেই আচমকা চোখ পরলো একটা শিরোনামের উপর। শিরোনামটি হচ্ছে ‘বায়ুদূষণে শীর্ষ ঢাকা’। আর্টিকেলটি পড়ে জানলাম, বিশ্বের ১২৫টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষে অবস্থান করছে ঢাকা। এ আর নতুন কি, প্রতিনিয়তই শোনা যায় দূষণের দিক দিয়ে সবসময় ঢাকাই সবার শীর্ষে থাকে। এছাড়াও, বর্তমানে নদী-খাল দূষণ ও দখল, জলাভূমি ভরাট, পাহাড় কাটা, বন উজাড় ইত্যাদি বিষয় নিয়মিতভাবে সংবাদ পত্রে স্থান পাচ্ছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের এই ধ্বংসযজ্ঞ উদ্বেগজনক ও অকল্পনীয়। ২০২৫ সালের বৈশ্বিক পরিবেশ সূচক (Environmental Performance Index-EPI) অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৯তম। এছাড়া, ২০২৫ সালের বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদন (IQAir) অনুসারে, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশ হিসেবে শীর্ষস্থান দখল করেছে। শব্দদূষণ ও পানিদূষণের অবস্থাও অত্যন্ত ভয়াবহ। গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত ৫৭ বছরে নদী দখল, দূষণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ এবং অপরিকল্পিত স্থাপনার কারণে ১৫৮টি নদী শুকিয়ে গেছে বা বিলুপ্তির পথে রয়েছে। (প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০২০) রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী, দেশের ৫৬টি নদী অতিমাত্রায় দূষণের শিকার, যার বেশির ভাগই শিল্পকারখানার বর্জ্য থেকে নির্গত দূষণ। দেশের ২২৯টি নদী দখল ও দূষণের কবলে পড়ে সংকটাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে গেছে। (প্রথম আলো, ২৬ মে ২০২৪) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ঢাকার বাতাসে ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান যেমন আর্সেনিক, সিসা ও ক্যাডমিয়ামের মাত্রা ডব্লিউএইচওর নির্ধারিত সীমার প্রায় দ্বিগুণ। (দ্য ডেইলি স্টার, ১১ মে ২০২৪) বায়ুদূষণের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব হলো এটি বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু প্রায় সাত বছর কমিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, বায়ুদূষণ ও অন্যান্য পরিবেশদূষণের কারণে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ ৭২ হাজার মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করছে। পরিবেশদূষণ শুধু স্বাস্থ্য, প্রকৃতি ও সমাজের উপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে না, এর অর্থনৈতিক প্রভাবও ব্যাপক। অথচ, এসব সমস্যা মোকাবিলায় বিচারব্যবস্থার কার্যকর ভূমিকা চোখে পড়ে না বললেই চলে। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়— আমাদের বিচারব্যবস্থা কি সত্যিই পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয়?
পরিবেশ সংরক্ষণ করা একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(ক) অনুযায়ী, রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে, এই অনুচ্ছেদটি সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশের অধিকার সরাসরি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত না হওয়ায় এটি বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়। তবে, উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী, সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জীবনের অধিকারের মধ্যে সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
দূষিত বাতাসে বসবাসের ফলে মানুষের গড় আয়ু হ্রাস পাওয়াকে সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে কিছু দুর্বলতা ও অসামঞ্জস্য রয়েছে, যা এর সঠিক বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের আইনি ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মামলা হলো ড. মহিউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশ (৪৯ ডিএলআর এডি ১৯৯৭)। এই মামলায় আদালত রায় দিয়েছে যে, বায়ু ও পানিদূষণমুক্ত একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার, যা ছাড়া জীবনের অধিকার পূর্ণতা পায় না। এই রায়ের আলোকে, ঢাকার দূষিত বাতাসে বসবাসের কারণে মানুষের গড় আয়ু কমে যাওয়াকে সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশের অধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর ফলে রাষ্ট্রকে আইনগতভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব।
পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের কিছু ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি সক্রিয় পদক্ষেপের চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার উপর বেশি জোর দেয়। আইনে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটি পরিবেশের অবক্ষয় রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। আইনটিতে ‘ইনজুরি থেরাপি’ মডেলের প্রতিফলন রয়েছে, যেখানে ক্ষতি হওয়ার পরেই ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।
উদাহরণস্বরূপ, আইনে পাহাড় কাটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের নামে পাহাড় কাটার অনুমতি দেওয়ার বিধানও রয়েছে। একইভাবে, জলাধার (নদী, খাল, হাওর) ভরাট নিষিদ্ধ করা হলেও জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে তা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (ধারা ৬: খ, ঙ)। তবে, ‘জাতীয় স্বার্থ’ শব্দটির কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা আইনে দেওয়া নেই, যা এর অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে। এর ফলে আইনসিদ্ধভাবেই জলাধার ভরাট বা পাহাড় কাটার মতো ক্ষতিকর কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণের নামে হাজার হাজার গাছ কাটার ঘটনা এই আইনের অপব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত নদ-নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং নদী রক্ষা কমিশনকে নদীগুলোর আইনি অভিভাবক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তবে, পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে জাতীয় স্বার্থের নামে জলাধার ভরাট ও পাহাড় কাটার বিধানটি আদালতের এই রায়ের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। যেহেতু নদীকে একটি আইনি সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাই জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে এর ক্ষতি বা দখল করা আদালতের রায়ের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের সংস্কার ও স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় এবং আইনের অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হয়।
পরিবেশদূষণ মোকাবিলায় বাংলাদেশের আইনি কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হলেও, এই ক্ষমতার ব্যবহারে জবাবদিহির কোনো স্পষ্ট ব্যবস্থা নেই। আইনে সরল বিশ্বাসে গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়মুক্তির বিধান থাকায়, পরিবেশের ক্ষতি রোধে ব্যর্থতা বা অবহেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায় না। এর ফলে পরিবেশদূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ফাঁক থেকে যায়।
পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারও সীমিত। এটি শুধুমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ এর অধীনে অপরাধের বিচার করতে পারে। অন্যান্য পরিবেশগত বিষয় যেমন বন, জীববৈচিত্র্য, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার সাধারণ আদালতে হয়, যা পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়াও, সাধারণ মানুষ সরাসরি পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন না। পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে হয়, যা প্রক্রিয়াটিকে জটিল ও সময়সাপেক্ষ করে তোলে। এই ব্যবস্থা পরিবেশগত অপরাধের প্রতিকার পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে।
পরিবেশ অধিদপ্তরের সীমিত জনবল ও আর্থিক সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় মামলা দায়ের করা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দূষণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, কিন্তু এর এখতিয়ার সীমিত হওয়ায় কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা যায় না। বেশিরভাগ মামলায় দূষণকারীরা আপিল করে ছাড় পেয়ে যায়। বাংলাদেশ আইন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ভ্রাম্যমাণ আদালতের ৯৮% মামলার রায় আপিলে বাতিল হয়ে যায়, যা পরিবেশদূষণ রোধে এই পদ্ধতির কার্যকারিতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।
জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সংস্থা (ইউএনইপি) এর মতে, বাংলাদেশে প্রচুর পরিবেশ আইন থাকলেও এর বাস্তবায়ন খুবই দুর্বল। পরিবেশগত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন স্পষ্ট, ন্যায্য ও বাস্তবায়নযোগ্য আইন, পরিবেশগত তথ্যে প্রবেশাধিকার, জনগণের অংশগ্রহণ এবং কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। তবে বাংলাদেশের পরিবেশ আইনে এই উপাদানগুলোর অভাব রয়েছে। আইনের অস্পষ্টতা, বাস্তবায়নে জবাবদিহির অভাব এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার ঘাটতি পরিবেশগত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পথে বড় বাধা।
পরিবেশ আইনের সংস্কার ও কার্যকর বাস্তবায়ন ছাড়া পরিবেশদূষণ রোধ করা সম্ভব নয়। পরিবেশগত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা গেলে শুধু পরিবেশই নয়, টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নও নিশ্চিত করা যাবে। পরিবেশ আইনের সংস্কার ও এর কার্যকর প্রয়োগ এখন সময়ের দাবি।